অথবা, বণিক সভ্যতা কিভাবে গ্রামীণ সভ্যতাকে বিপর্যস্ত করেছে তা ‘পথ জানা নাই’ গল্প অবলম্বনে আলোচনা কর।
অথবা, আধুনিক বণিক সভ্যতা কীভাবে মাউলতলা গ্রামের লোকজ শাশ্বত জীবন হরণ করেছে তা শামসুদ্দীন আবুল কালাম এর ‘পথ জানা নাই’ গল্প অনুসরণে আলোচনা কর।
উত্তর৷ ভূমিকা : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতম সময়ের সার্থক গল্পকারদের মধ্যে শামসুদ্দীন আবুল কালাম তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও শৈল্পিক গুণাবলিতে সমুজ্জ্বল। তাঁর রচিত গল্প-উপন্যাসে জীবনের সূক্ষ্মতম যন্ত্রণার প্রকাশ যেমন ঘটেছে তেমনি প্রকাশ ঘটেছে সমাজ বিশ্লেষণের। ঔপন্যাসিকের ‘পথ জানা নাই’ গল্পটি সমাজ বিশ্লেষণের একটি প্রামাণ্য দলিল। এই গল্পে আধুনিক বণিক সভ্যতা কীভাবে একটি নিস্তরঙ্গ সরল সহজ গ্রামীণ সমাজকে বিপর্যস্ত করেছে তা লেখক বাস্তবভিত্তিক কাহিনির মধ্য দিয়ে বর্ণনা করেছেন। গল্পটি এ কারণে সমসাময়িক সভ্যতার নগ্নতার প্রতি তীব্র কটাক্ষ ।
গ্রাম ও নগর : একদিকে অগণিত গ্রাম আর একদিকে স্বল্প সংখ্যক শহর বা নগর নিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের বাংলাদেশ। গ্রামের তুলনায় শহরের সংখ্যা যেমন সীমিত, লোকসংখ্যার বিভাজনও তেমনি অসমানুপাতিক। সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি আমাদের জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ বসবাস করে আসছে গ্রামে। গ্রামই আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পাদপীঠ । আমাদের জীবন ঘরানার মৌল বৈশিষ্ট্যটি খুঁজে পাওয়া যায় গ্রামেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশের নগরসমূহ হয়ে উঠেছে আধুনিক জামানার সবকিছুর ধারক-বাহক। আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে সামান্য হলেও বিশাল গ্রামসাম্রাজ্যের চালিকাশক্তি এখন শহরের হাতে। তাই গ্রামের মানুষ তাদের জীবনের দিক নির্দেশনা পাওয়ার জন্য তাকিয়ে থাকে শহরের দিকে। শহুরে বণিক সভ্যতার সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে চেষ্টা চালায় জীবন ও জীবিকার উন্নয়ন সাধনের। এই প্রচেষ্টার ফল সবসময় যে ইতিবাচক হয় তা নয়। এর নেতিবাচকতা সম্পর্কে শামসুদ্দীন আবুল কালাম ‘পথ জানা নাই’ গল্পে বাস্তবভিত্তিক আলোচনা করেছেন।
গ্রামীণ জীবনব্যবস্থা : বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন চিরকালই নিস্তরঙ্গ। এখানে শান্তি ও স্বস্তি বিনামূল্যে বিতরণ হয়। ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় এই ছোট-বড় গ্রামগুলোতে মায়ের স্নেহ, পিতার আদর, ভায়ের ভালোবাসা, বোনের মমতা, প্রতিবেশির সহানুভূতি প্রভৃতির অভাব নেই। এখানকার মানুষেরা সহজ সরল ও অকপট। এখানকার গাছ-গাছালি লতাপাতার শ্যামলিমার মতোই কোমল এখানকার মানুষের মন। এরা অপরের সুখে হাসে এবং অপরের দুঃখে কাঁদে। হিংসা বিদ্বেষ লড়াই ফ্যাসাদকে এরা এড়িয়ে চলে। কোনও কারণে এর ব্যত্যয় দেখা দিলে নিজেরাই বসে মীমাংসা করে নেয়। পারতপক্ষে কেউ আইন-আদালত ও থানা- পুলিশের শরণাপন্ন হতে চায় না। অল্পে তুষ্ট থাকে বলেই এদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি ও খুনোখুনি নেই বললেই চলে। জীবন সম্পর্কে গ্রামের মানুষ প্রকৃতি ও ঈশ্বরনির্ভর। এরা সুখ, শান্তি ও স্বস্তিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এ কারণে এদের জীবন ধারণের ক্ষেত্রে চাহিদা কম ।
নাগরিক বণিক সভ্যতা : গ্রামীণ জীবনের তুলনায় নাগরিক জীবন সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ও বিপরীতধর্মী। শহরের মানুষ আত্মকেন্দ্রিক ও লোভী। পরশ্রীকাতরতা শহরের লোকদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষের জন্ম দেয়। তাই অল্পে এরা খুশি থাকতে পারে না। শহরের মানুষদের মনমানসিকতা বাণিজ্যিক। বণিক সভ্যতা এদেরকে উচ্চাভিলাসী করে ফেলেছে। এরা অল্পে তুষ্ট নয়। বেশি বেশি চাহিদার কারণে শহরের মানুষ হিংস্র হয়ে উঠে। এ কারণে এদের মধ্য থেকে মানবিকতা লোপ পায়। আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য এরা হন্যে হয়ে উঠে
মাউলতলার পূর্বাবস্থা : মাউলতলা দক্ষিণ বাংলার একটি নিভৃত গ্রাম। অন্য দশটি গ্রামের মতো এখানকার মানুষ ছিল শান্তি প্রিয়। গ্রামের মানুষ মিলে মিশে হাসি আনন্দে দিন কাটাত। মামলা-মকদ্দমা, রোগব্যাধি এ গ্রামে বলতে গেলে ছিলই না। এই নিস্তরঙ্গ গ্রামে সুখ, শান্তি, স্বস্তি ও আনন্দের অভাব ছিল না। হিংসা বিদ্বেষ ছিল অনুপস্থিত।
বণিক সভ্যতার অনুপ্রবেশ : মাউলতলা গ্রামের জোনাবালি বাইরে থেকে গ্রামে ফিরে এসে গ্রামবাসীকে শোনাল নতুন জীবনের কথা। শহরের সাথে গ্রামের যোগাযোগ স্থাপিত না হলে জীবনের ও জীবিকার উন্নতি হবে না- এ কথাটা সে গ্রামবাসীকে বুঝাতে সক্ষম হলো। কারো কারো আপত্তি সত্ত্বেও গ্রামের মানুষের জমির উপর দিয়ে নির্মিত হলো একটি সড়ক। এই সড়ক দিয়ে শহরে যাতায়াত করা শুরু হলো। গহুরালির পাঁচ কুড়া জমির দুই কুড়াই চলে গেল সড়কে। তবুও নতুন জীবনের স্বপ্নে বুক বেঁধে দাঁড়াল সে।
বণিক সভ্যতার প্রভাব : নির্মিত নতুন সড়কের মাধ্যমে শহুরে বণিক সভ্যতার সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠল মাউলতলার। এর ফলে কেবল গহুরালির জীবনেই পরিবর্তন এল না, এল গোটা গ্রাম্য জীবনেই। তবে সেই পরিবর্তনের প্রায় সবটুকুই নেতিবাচক। সামান্য কারণেই মানুষ আইন-আদালত শুরু করল। শোনা গেল মন্বন্তরের পদধ্বনি। দাম বাড়ল সব জিনিসের, কমল কেবল জীবনের দাম। গ্রামে এল রোগব্যাধি, চোরাবাজারি ও ঠিকাদারি। সুশাসনে নিযুক্ত কর্মচারী নতুন সড়ক বেয়ে গ্রামে আসতে লাগল আর ফিরে যেতে লাগল ঘুষের টাকায় পকেট ভর্তি করে। শহরের বাবুর্চিখানার লুৎফর আসগরউল্লাহর সোমত্ত মেয়ে কুলসুমকে নিয়ে পালাল। যুদ্ধ ফেরৎ ইউসুফের স্ত্রী কঠিন স্ত্রীরোগে আক্রান্ত হলো। আর আসতে লাগল তরিতরকারি কাঠ-মুরগি, শাকপাতা কেনার ঠিকেদার। গহুরালির শখ্য গড়ে উঠল এক মিলিটারির দালালের সাথে। তার সাথে ব্যবসায় করে গহুরালির আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলো। খড়ের ঘরের পরিবর্তে ভিটেয় উঠল টিনের ঘর। কিন্তু একদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে গহুরালি দেখল তার স্ত্রী হাজেরা ঘরে নেই। খোঁজ নিয়ে বুঝতে পারল ওই দালালের সাথে হাজেরা পালিয়েছে। মন্বন্তরে গহুরালি নিঃস্ব হয়েছিল বাইরে, এবার হলো অন্ত রে। বণিক সভ্যতা এভাবে একটা নিস্তরঙ্গ গ্রামকে বিপর্যস্ত করে ফেলল।
উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বণিক সভ্যতার কুফল মাউলতলা গ্রামটিকে তচনচ করে দিয়েছিল। এখানকার মানুষের নিস্তরঙ্গজীবনে এই সভ্যতা যে তরঙ্গ তুলেছিল তাতে গ্রামের লাভের চেয়ে ক্ষতি হয়েছিল বেশি। বণিক সভ্যতার নগ্নতা শান্তশিষ্ট স্নিগ্ধ গ্রামটিকে অস্থির করে তুলেছিল। এ গ্রামের মানুষের সুখশান্তিকে কেড়ে নিয়ে তাদেরকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল।
শামসুদ্দীন আবুল কালামের ‘পথ জানা নাই’ গল্প অবলম্বনে বণিক সভ্যতা পাশ কানুন কীভাবে একটি নিস্তরঙ্গ সরল গ্রামকে বিপর্যস্ত করেছে তা আলোচনা কর।
পরবর্তী পরীক্ষার রকেট স্পেশাল সাজেশন পেতে হোয়াটস্যাপ করুন: 01979786079
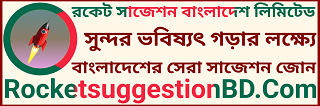
Leave a Reply