উত্তর৷ ভূমিকা : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) জীবন সায়াহের অন্যতম কবিতা ‘ঐকতান।’ এ কবিতায় কবির অন্তিম ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যসাধনার ফলে বিশ্বদরবারে তিনি প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এ কবিতায় তিনি নিজের সাহিত্যসাধনার আদর্শগত দিক আলোকপাত করেছেন।
সমকালীন সাহিত্যের ধারা : বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের ফলে সাহিত্যের সকল শাখা পারিত হয়ে উঠেছে। তবে ত্রিশোত্তর কবিদের অনেকেই রবীন্দ্রবলয় ভেদ করবার চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথই বাঙালি শিক্ষিত শ্রেণির প্রতিভূ ছিলেন। রবীন্দ্র সমকালে এদেশের আর্থসামাজিক অবস্থা ভালো ছিল না। তারপরও তিনি এদেশের মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মিছিলে যোগ দেননি। তাঁর কাব্যে ভাবদর্শন, প্রকৃতি প্রেম ও অধ্যাত্মবাদ ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছিল। ত্রিশোত্তর কবিরা ইতিহাস ও ঐতিহ্যানুসারী হলেও রচনারীতিতে ছিলেন পাশ্চাত্যানুসারী।
সাহিত্যসাধনা সম্পর্কে কবির অভিমত : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সাহিত্যসাধনা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সে সাথে নিজের সাহিত্য সম্পর্কে নিজেই মূল্যায়ন করেছেন। কারণ নিজে যা সৃষ্টি করেছেন, সমকালীন কবিরা যা সৃষ্টি করেছেন তার সাথে মূল্যায়ন করতে গিয়ে অপূর্ণতা খুঁজে পেয়েছেন। তাই কবি ‘ঐকতান’ কবিতায় সাহিত্যের আদর্শ মূল্যায়নের স্বরূপ সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।
কবির বিশ্বসন্দর্শন : কবি হিসেবে সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করতে হলে বিশ্বদৃষ্টি জরুরি। বিশ্বায়ত চিন্তাধারায় বিকাশ লাভ করতে হলে বিশ্বসভ্যতা, প্রকৃতি, মানুষ, মনুষ্যকীর্তি ও ভৌগোলিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ দরকার। বিশ্বভাবনার মাধ্যমে আত্মিক উন্নয়ন সম্ভব। বিশ্বায়ত জ্ঞান লাভ পরিভ্রমণের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে সম্ভব নয়। গ্রন্থপাঠের মাধ্যমে বিশ্বায়ত জ্ঞানলাভ সম্ভব। সাহিত্যে বিশ্বমানবতার সুর বেজে না উঠলে সে সাহিত্য জড় সাহিত্য হতে বাধ্য। সাহিত্যে কল্পলোকের কোন সীমাবদ্ধ গণ্ডি নেই, নেই কোন পরিসীমা। কবি বলেন-
‘সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে,
তার কোন পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে
অন্তরের অনুসন্ধান : বিশ্বায়ত অন্তর অনুভূতি একমাত্র হৃদয় দিয়ে সম্ভব। কেননা, এ হৃদয়ালোকের সন্ধান কেবল হৃদয় স্পর্শ দিয়ে লাভ করা যায়। কবি যথার্থই বলেছেন-
‘অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়
পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার।
সর্বসাধারণের জন্য সাহিত্য : কবির বিশ্বভাবনা বিশ্বায়ত চেতনালোকে সমগ্র বিশ্বকে তাঁর সাহিত্যে স্থান দিতে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। শ্রেণি বৈষম্যের কারণে তাঁর সাহিত্য সর্বজনীনতা অর্জনে ব্যর্থ। কবি জীবনসায়াহ্নে কামার কুমার তাঁতী কৃষক ও দিনমজুর মানুষের জীবন চিত্রকে সাহিত্যানুষঙ্গ করার প্রেরণায় উন্মুখ ছিলেন।
মাটিঘেঁষা কবির প্রতি আহ্বান : মানুষের কবি ব্যতীত গ্রামবাংলার জীবনঘনিষ্ঠ সাহিত্য রচনা করা সম্ভব নয়। একমাত্র লৌকিক কবিই পারেন সাধারণ মানুষের কাছাকাছি যেতে। শ্রেণি চরিত্র, শ্রেণি চেতনা ও জীবন বাস্তবতা সম্পর্কে অনুমাননির্ভর সাহিত্য জীবন সত্যকে ধারণ করে না। কবি বলেছেন-
‘যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।’
শুধু শিল্পকুশলতা কাম্য নয়: সাহিত্য মানবজীবনের দর্পণ। শিল্পগুণসমৃদ্ধ সাহিত্য সকলের পাঠযোগ্য। কিন্তু এ ধরনের সাহিত্যের সাথে মানবজীবনের কোন সম্পর্ক নেই। দারিদ্র্যক্লিষ্ট খেটে খাওয়া মানুষের জীবনচিত্র এ সাহিত্যে নেই। শিল্পকুশলতার বিপক্ষে অবস্থান করে কবি বলেছেন-
‘সত্য মূল্য না দিয়ে সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভাল নয়, ভাল নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি।
সাহিত্য আনন্দের উপাদান : নিরানন্দ জীবনকে আনন্দে ভরপুর করে দিতে পারে একমাত্র সাহিত্য। সাহিত্য আনন্দের উল্লেখযোগ্য উপাদান। বৃহত্তর গোষ্ঠীর হৃদয়কে পুলকিত ও আন্দোলিত করতে পারে সাহিত্য। শিক্ষিত শ্রেণির হৃদয়কে আন্দোলিত করতে পারলেই কেবল সাহিত্য তার উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হয়।
বাউল কবিদের প্রতি সম্মান : নাগরিক সভ্যতার ভিড়ে গ্রামবাংলার আউল বাউল কবিরা স্বীকৃতি পান না। অবহেলা আর অনাদরের মধ্যে তাঁরা সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হন। এসব নিভৃতচারী কবি সভ্য সমাজে পরিচিত নন। কিন্তু সম্মানটুকু তাদের প্রাপ্য। নিভৃতচারী কবিদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-
“আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।”
উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নিজের সাহিত্যের সীমা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাঁর সাহিত্যে রোমান্টিকতার অন্তরালে ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজসভ্যতা প্রকাশ পেয়েছে। ‘ঐকতান’ কবিতাটিতে কবির জীবনবোধের স্বরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে।
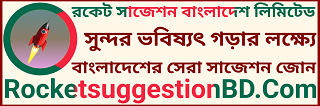
Leave a Reply