অথবা, প্রমথ চৌধুরী সামাজিক জীবনে কেন যৌবনের প্রতিষ্ঠা চান? প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতিতিনি কেন সমালোচনামুখর?
অথবা, “আমরা যে যৌবনকে গোপন করে রাখতে চাই তার জন্য আমাদের প্রাচীন সাহিত্য অনেক পরিমাণে দায়ী”– যৌবনে দাও রাজটিকা’ প্রবন্ধ অবলম্বনে উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
অথবা, প্রমথ চৌধুরীর ‘যৌবনে দাও রাজটিকা’ প্রবন্ধে সংস্কৃত কাব্যের দুর্বলতার যে দিকটি চিহ্নিত হয়েছে তা নিজের ভাষায় লিখ।
অথবা, ‘যৌবনে দাও রাজটিকা’ প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী এদেশের পণ্ডিতদের সমালোচনা করেছেন কেন তা নিজের ভাষায় লিখ।
উত্তর৷ ভূমিকা : আপন প্রতিভা ও প্রভায় বাংলা গদ্যশৈলীকে যিনি বিশিষ্টতা দান করেছেন, তিনি হলেন প্রমথ চৌধুরী। ‘সবুজপত্র’ প্রকাশ করে তিনি অভিনব রচনারীতির যেমন প্রচলন করেন, তেমনি সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সংস্কারমুক্ত প্রগতিশীলতার পরিচয় দেন। তারুণ্যের জয়গানে তিনি ছিলেন যৌবনধর্মের অগ্রদূত এবং যুক্তিনিষ্ঠ আধুনিক। এ অভিজাত চিন্তাশীল লেখকের অসাধারণ সৃষ্টি ‘যৌবনে দাও রাজটিকা প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে তিনি যৌবনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের যৌবনচিন্তার তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। সংস্কৃত ভাষার সাহিত্যিকরা ছিলেন ভোগবাদী। যৌবনকে তাঁরা দেখেছেন ভোগের সামগ্রী হিসেবে। এ কারণে তাঁরা যৌবন নিন্দায় পঞ্চমুখ ছিলেন। প্রাবন্ধিক তাঁদের যৌবন চিন্তার তাৎপর্য তুলে ধরে স্বীয় চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন এ প্রবন্ধে।
সংস্কৃত সাহিত্যে যৌবন : আমরা যে যৌবনকে গোপন করে রাখতে চাই তার জন্য দায়ী আমাদের প্রাচীন সাহিত্য। সংস্কৃত সাহিত্যে দৈহিক যৌবনের বিচিত্র লীলাকলা সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা লক্ষ করা যায়। এ সাহিত্যে যুবক-যুবতী ব্যতীত আর কারও স্থান নেই। যৌবনের যে ছবি সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে ফুটে উঠেছে, সে হচ্ছে ভোগবিলাসের চিত্র। সংস্কৃত কাব্যজগৎ মাল্যচন্দন বনিতা দিয়ে গঠিত, আর এ জগতের বনিতাই হচ্ছে স্বর্গ এবং মাল্যচন্দন তার উপসর্গ। এ কাব্য জগতের স্রষ্টা কিংবা দ্রষ্টা কবিদের মতে প্রকৃতির কাজ হচ্ছে শুধু রমণী দেহের উপমা যোগান, পুরুষের কাজ শুধু রমণীর মন যোগান। যযাতি নিজের ভোগ বিলাস চরিতার্থ করার জন্য পুত্রদের কাছে যে দৈহিক যৌবন ভিক্ষা করেছিলেন সংস্কৃত কবিরা সে যৌবনেরই রূপগুণ বর্ণনা করেছেন।
যারা যৌবনকে নিন্দা করে : প্রাচীনপন্থি সংস্কৃত সাহিত্যের স্রষ্টারা যৌবন নিন্দায় পঞ্চমুখ ছিলেন। কারণ তারা যৌবনকে কেবল ভোগের মোক্ষম সময় বলে মনে করতেন। যৌবন যে সৃষ্টির প্রধানতম বাহন তা তারা জানতেন না। ভোগ ও লালসার মাধ্যম হিসেবে যৌবনকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে এরা যৌবন ভয়ে ভীত থাকতেন। তাই যযাতি নিজের পুত্রের কাছে যে যৌবন ভিক্ষা করেছিলেন সে যৌবনকে এঁরা ভিন্ন দৃষ্টিতে অবমূল্যায়ন করেছেন।
যৌবন নিন্দার কারণ : সংস্কৃত সাহিত্যে দেহকে অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ কারণে যৌবন সেখানে ভোগের মোক্ষম উপকরণ। এ যৌবন ক্ষণস্থায়ী বলেই যৌবনের নিন্দায় সংস্কৃত সাহিত্য মুখর। যাঁরা স্ত্রীজাতিকে কেবল ভোগের সামগ্রী বলে মনে করেন তাঁরাই স্ত্রী-নিন্দায় ওস্তাদ। এর প্রমাণ সকল সাহিত্যে নিত্য পাওয়া যায়। স্ত্রী-নিন্দুকের রাজা হচ্ছেন রাজকবি ভর্তৃহরি ও সোলেমন। চরম ভোগবিলাসে পরম চরিতার্থতা লাভ করতে না পেরে এঁরা শেষ বয়সে স্ত্রীজাতির উপর গায়ের ঝাল ঝেড়েছেন। যাঁরা বনিতাদেরকে মাল্যচন্দন হিসেবে ব্যবহার করেন তাঁরা শুকিয়ে গেলে সে বনিতাদেরকে মাল্যচন্দনের ন্যায়ই ভূতলে নিক্ষেপ করেন। এদেরকে পদদলিত করতেও এঁরা পিছপা হন না। প্রথম বয়সে মধুর রস অতিমাত্রায় চর্চা করলে শেষ বয়সে জীবন তেতো হয়ে উঠে। এ শ্রেণির মানুষ ভোগলালসায় অতৃপ্ত থেকেই বৈরাগ্য সাধনে নেমে পড়েন। একই কারণ বর্তমান যৌবননিন্দার ক্ষেত্রেও। যাঁরা যৌবনকে কেবল ভোগের উপকরণ হিসেবে মনে করেন তাঁদের মুখেই যৌবননিন্দা লেগে থাকে। যাঁরা যৌবন জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেন, তাঁরা ভাটার সময় পাঁকে পড়ে গত জীবনের প্রতি কটুকাটব্য প্রয়োগ করেন। যৌবনের উপর তাদের রাগের কারণ এই যে তা পালিয়ে যায়, একবার চলে গেলে আর ফেরে না।
প্রমথ চৌধুরীর যৌবন চিন্তার স্বরূপ : প্রমথ চৌধুরী সংস্কৃত সাহিত্যের যৌবন-চিন্তার ঘোর বিরোধী। তিনি যৌবনকে দেখেছেন প্রাণশক্তি হিসেবে। এ কারণেই তিনি যৌবনের কপালে রাজটিকা পরানোর প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁর মতে, ‘যৌবনে মানুষের বাহ্যেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় সব সজাগ ও সবল হয়ে উঠে, এবং সৃষ্টির মূলে যে প্রেরণা আছে মানুষ সে প্রেরণা তার সকল অঙ্গে, সকল মনে অনুভব করে। —দেহের যৌবনের সাথে মনের যৌবনের একটা যোগাযোগ থাকলেও দৈহিক যৌবন ও মানসিক যৌবন স্বতন্ত্র। এ মানসিক যৌবন লাভ করতে পারলেই আমরা তা সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পারব। — একের দেহের যৌবন অপরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার জো নেই; কিন্তু একের মনের যৌবন লক্ষ লোকের মনে সংক্রমণ করে দেওয়া যেতে পারে।’ প্রমথ চৌধুরী মানসিক যৌবনের পূজারী। তিনি এ যৌবনকে সমাজের বুকে অভিষিক্ত করতে আগ্রহী। যে সমাজে মানসিক যৌবন নেই সে সমাজ অথর্ব, পঙ্গু। আমাদের দায়িত্ব সমাজের বুকে মানসিক যৌবনের উন্মাদনা সৃষ্টি করা। যদি তা সম্ভব হয় তবে সে সমাজের মানসিক যৌবনের কপালে রাজটিকা পরিয়ে দিতে হবে।
উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ভোগবাদী সংস্কৃত সাহিত্য যৌবনের অবমূল্যায়ন করেছে ভোগের লালসা থেকেই। এ কারণে এ সাহিত্য যৌবনের নিন্দায় পঞ্চমুখ। কিন্তু যৌবন নিন্দার সামগ্রী নয়। যৌবন সমাজ ও সভ্যতার চালিকাশক্তি।
যৌবনে দাও রাজটিকা’ প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী যৌবনের প্রতি এদেশের পণ্ডিতদের যে মনোভাবের কথা বলেছেন তা আলোচনা কর।
পরবর্তী পরীক্ষার রকেট স্পেশাল সাজেশন পেতে হোয়াটস্যাপ করুন: 01979786079
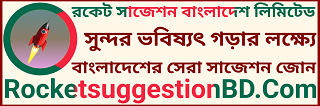
Leave a Reply