অথবা, ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধানুসারে লেখকের বিশ্বাসভঙ্গের কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর।
উত্তরা৷ ভূমিকা : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর আশিতম জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে পাঠ করার উদ্দেশ্যে ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কিত নিজস্ব মূল্যায়ন তিনি সকলকে জানানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন বলেই এ নিবন্ধের অবতারণা। কৈশোর থেকে কবির মধ্যে যে পাশ্চাত্যপ্রীতির প্রতি দুর্বলতা লক্ষ করা গেছে বার্ধক্যে এসে তার স্খলনের ব্যাখ্যা তিনি এ প্রবন্ধে বর্ণনা করেছেন। প্রবন্ধটিকে কবির আত্মসমালোচনার দলিল বলেও অভিহিত করা যায়। এখানে তিনি নিজের অনুভূতিকে নির্দ্বিধায় নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করেছেন।
পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ : মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় বুকে ধারণ করে পাশ্চাত্য সভ্যতার জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল পশ্চিম দিগন্ত থেকে। মানবতাবাদী শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও সংস্কৃতির প্রদর্শনী করে তারা সমগ্র পৃথিবীতে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তখন সারা বিশ্ব ইউরোপীয় সভ্যতার ভূয়সী প্রশংসায় মেতে উঠেছিল। দেশে দেশে গৃহীত ও সমাদৃত হয়েছিল ব্যাপকভাবে। সনাতনপন্থি ভারতবর্ষও ইংরেজ সভ্যতার মহত্ত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিল দ্বিধাহীন চিত্তে। সে সময় প্রকৃতিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞের সংখ্যা ছিল অল্প। ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যকে পরিচয়। দিনরাত্রি মুখরিত ছিল বার্কের বাগ্মিতায়, মেকলের ভাষা প্রবাহের তরঙ্গভঙ্গে; নিয়তই আলোচনা চলত শেক্সপিয়ারের নাটক নিয়ে, বায়রনের কাব্য নিয়ে এবং তখনকার রাজনীতিতে সর্বমানবের বিজয় ঘোষণায়। তখন ভারতীয়রা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করলেও তাদের অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস।
পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস : ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে, একসময় ভারতীয় সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে এ বিজিত ভারতীয় জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী ইংরেজ জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেননা, সে সময় অত্যাচার-প্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংল্যান্ড। তাদের প্রত্যাশা ছিল ন্যায়বিচার ও ন্যায় শাসনের। মানবমৈত্রীর যে বিশুদ্ধ পরিচয় ইংরেজ চরিত্রে প্রতিভাত হয়েছিল তাতে এ বিশ্বাস রাখাটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ তখনও সাম্রাজ্য মদমত্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয়নি। বিশ্বমানবতাবোধের ঐশী বাণী তারাইতো পৌঁছে দিয়েছিল পৃথিবীর দেশে দেশে। তাই সনাতনপন্থি ভারতীয়রা অকপটে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এ সভ্যতার উপর। অথচ একদিন যে এ বিশ্বাসের পাহাড় ভেঙে খান খান হয়ে যাবে তা তারা ভুলেও ভাবতে পারেনি। একদিন তাই যখন সত্য হলো তখন স্তম্ভিত হলো গোটা ভারতবর্ষ।
রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স যখন অল্প ছিল তখন তিনি পড়াশোনা করতে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। সে সময় জন ব্রাইটের মুখ থেকে পার্লামেন্টে এবং তার বাইরে কোন কোন সভায় যে বক্তৃতা তিনি শুনেছিলেন তাতে ছিল চিরকালের ইংরেজদের বাণী। সেসব বক্তৃতায় হৃদয়ের ব্যাপ্তি জাতিগত সকল সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা তিনি যেমন ভুলতে পারেন নি তেমনি জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়েও তাঁর পূর্বস্মৃতিকে তা রক্ষা করেছে। এ পরনির্ভরতা নিশ্চয়ই শ্লাঘার বিষয় ছিল না বলে তিনি মনে করতেন। এর মধ্যে এটুকু প্রশংসার বিষয় ছিল যে, ভারতীয়দের আবহমানকালের অভিজ্ঞতার মধ্যেও মনুষ্যত্বের যে একটি মহৎ রূপ সেদিন দেখা গিয়েছিল তা ইংরেজদের আশ্রয় করে প্রকাশিত হলেও তাকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করার শক্তি তাদের ছিল। কারণ মানুষের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীর্ণভাবে কোন জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, তা কৃপণের অবরুদ্ধ ভাণ্ডারের সম্পদ নয় বলেই লেখক বিশ্বাস করতেন। এসব কারণেই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা ছিল।
মোহাচ্ছন্ন রবীন্দ্রনাথ : পাশ্চাত্য সভ্যতার উপকরণসমূহ এমন সমৃদ্ধ ছিল যে রবীন্দ্রনাথ তার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ইংরেজি ভাষাচর্চার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্যের আলোকে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতার দিকে তাকানোর সময় তাঁর ছিল না। তাইতো নোবেল বিজয়ীর গৌরব অর্জন করা। সত্ত্বেও দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর তেমন কোন অংশগ্রহণ আমাদের চোখে পড়ে না। তিনি মনে করতেন ইংরেজরা একদিন ঔদার্য প্রদর্শন করে ভারতীয়দের স্বাধীনতা উপহার দিয়ে ভারত ছেড়ে যাবে। কিন্তু অচিরেই তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। অচিরেই তাঁর মোহভঙ্গ ঘটে।
রবীন্দ্রনাথের মোহভঙ্গ : নিজস্ব সাহিত্যানুরাগ ইংরেজকে উচ্চাসনে বসিয়েছিল বলে লেখকের বিশ্বাস। কিন্তু এরপর মোহভঙ্গ আরম্ভ হলো কঠিন দুঃখে। প্রত্যহ তিনি দেখতে পেলেন, সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিতরূপে স্বীকার করেছে, রিপুর তাড়নায় তারা তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘন করে গেল। তাই নিভৃতে সাহিত্যের রসসম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন থেকে একদিন তাঁকে বেরিয়ে আসতে হলো। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য তাঁর চোখে পড়ল তাতে পাশ্চাত্যপ্রীতির মোহভঙ্গ ঘটল সাথে সাথে। এক অন্তহীন মর্মবেদনায় আচ্ছন্ন হলেন রবীন্দ্রনাথ।
রবীন্দ্রনাথের মর্মবেদনা : দিব্য চোখে লেখক দেখতে পেলেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জেগে উঠা মানবপীড়নের মহামারি দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই জীবনের প্রথম আরম্ভে ইউরোপের অন্তরের সম্পদ এ সভ্যতাকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন বলে তিনি আক্ষেপ করেছেন। জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তাঁর বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। এ বিশ্বাস ভঙ্গের মর্মবেদনাই এ প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে আর্তনাদ করে উঠেছে। এ চরম সত্যকে লেখক নির্দ্বিধায় অন্তহীন বেদনার সাথে চিত্রিত করেছেন। বিশ্বাসভঙ্গের মর্মবেদনাটি তাঁর আত্মসমালোচনার আঙ্গিকে প্রকাশ পেয়েছে।
উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার পেক্ষিতে বলা যায় যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার মানবতাবাদী উপকরণসমূহ লেখককে তার প্রতি সীমাহীন আনুগত্যে বন্দী করে রেখেছিল। যখন সে সভ্যতার নগ্নরূপটি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তখন তাঁর মর্মবেদনার আর অবধি ছিল না। একথা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন।
আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল”— এ উক্তিটিতে রবীন্দ্রনাথ যে মর্মবেদনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।
পরবর্তী পরীক্ষার রকেট স্পেশাল সাজেশন পেতে হোয়াটস্যাপ করুন: 01979786079
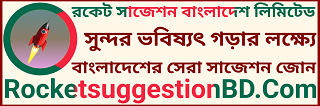
Leave a Reply