অথবা, চৈতন্য জীবনীসাহিত্য সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা কর।
অথবা, চৈতন্য চরিত সাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয় দাও।
উত্তর।৷ ভূমিকা : চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলার সাহিত্য ও সমাজজীবনে এক যুগান্তকারী ঘটনা। লোকোত্তর প্রতিভা ও চরিত্রের অধিকারী চৈতন্যদেবে সমকালীন জীবনধারায় যে পরিবর্তনের স্রোত এনে দিয়েছিলেন, তার প্রভাব একালেও মন্দীভূত হয়নি। তাই তাঁর সমকালেই তাঁর লৌকিক জীবনকাহিনী অলৌকিকায় মণ্ডিত হয়ে ভক্তজনের হৃদয়ে গভীর আবেগের সৃষ্টি করেছিল এবং তারই ফলোদয় ঘটেছিল বিভিন্ন সাহিত্যকৃতিতে চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছেন অথবা তাঁর সহচরদের সাহচর্যে এসেছেন, এমন অনেকেই চৈতন্যজীবনী চৈতন্যভাবধারার পরিচয় দানের জন্য তাঁর প্রায় সমকালেই লেখনী ধারণ করেছিলেন।এবং বহুশ্রুত চৈতন্য জীবনকাহিনীর প্রামাণিক উপাদান সংগ্রহ তৎকালে কোনো দুঃসাধ্য কর্ম ছিল না, কিন্তু চৈতন্যচরিতকারগণ সকলেই ছিলেন নৈষ্ঠিক চৈতন্যভক্ত, ফলে ভক্তের দৃষ্টিতে তাঁরা প্রভু জীবনকে নিরীক্ষণ করেছিলেন বলেই চৈতন্যজীবনীগুলি খাঁটি ‘জীবনীসাহিত্য’ হয়ে উঠতে পারেনি। অলৌকিকতায় মণ্ডিত চৈতন্যজীবনীগুলি প্রকৃতপক্ষে ‘সন্ত-সাধক-জীবনী’ রূপেই অভিহিত হবার যোগ্য।
বিশেষ রচনা : বাংলাভাষায় রচিত চৈতন্য জীবনীর সংখ্যা অপরিমিত না হলেও এদের প্রতিটিই সুলিখিত এবং প্রতিটিই কোনো-না-কোনো কারণে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এদের মধ্যে বৃন্দাবনদাস-রচিত ‘চৈতন্যভাগবত’ এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ বৈষ্ণব সমাজে শুধু বিশিষ্টতাই লাভ করেনি, একেবারে ধর্মগ্রন্থের মর্যাদায়ও অভিষিক্ত হয়েছে। অপর গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে লোচনদাসের ‘চৈতন্য মঙ্গল’, জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গল’’, ‘গোবিন্দদাসের কড়চা’ এবং চূড়ামণিদাসের ‘গৌরাঙ্গবিজয়’।
চৈতন্যভাগবত : বাংলাভাষায় রচিত চৈতন্যজীবনীগুলোর মধ্যে বৃন্দাবনদাস রচিত ‘চৈতন্যভাগবত’ই সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীন। বৃন্দাবনদাসের মায়ের নাম নারায়ণী, পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত; তবে প্রভু নিত্যানন্দ ছিলেন বৃন্দাবনদাসের গুরু। তিনি গুরুর কাছ থেকে চৈতন্যজীবনীর উপাদান জ্ঞাত হয়েছিলেন বলে তাঁর বর্ণিত তথ্যে আস্থা স্থাপন করা চলে । গ্রন্থ রচনাকাল বিষয়ে নিশ্চিতভাবেই কিছু বলা না গেলেও পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দের আগেই হয়তো গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। ‘চৈতন্যভাগবত’ তিনখণ্ডে বিভক্ত। এর আদিখণ্ড চৈতন্যদেবের গয়া থেকে প্রত্যাবর্তন, মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাসগ্রহণ এবং অভ্যখণ্ডে চৈতন্যদেবের নীলাচলে গুণ্ডিচাযাত্রা পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কবিরাজ কৃষ্ণদাস মনে করেন যে, নিত্যানন্দ লীলা বর্ণনায় আবিষ্ট হয়ে পড়ায় বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবের শেষ লীলা বর্ণনা করে উঠতে পারেননি। বৃন্দাবনদাস মোটামুটিভাবে ভাগবতপুরাণের অনুসরণেই চৈতন্যলীলা বর্ণনা করেছেন বলে তাঁকে ‘চৈতন্যলীলার ব্যাস’ বলে অভিহিত করা হয়।কৃষ্ণলীলার অনুসরণ হেতু চৈতন্য ভাগবতে বহু অলৌকিক এবং অপ্রাকৃত বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও গ্রন্থটি অতিশয় উপাদেয় বলে বিবেচিত হয়। এর সহজ সরল ভাষা এবং বিভিন্ন চরিত্র চিত্রাঙ্কনে স্বাভাবিকভাবেই এর প্রধান আকর্ষণ। এ ছাড়া সমকালীন নবদ্বীপ সমাজের যে তথ্যনিষ্ঠ বাস্তবচিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। এই সমস্ত কারণে সাধারণ পাঠকের নিকট বৃন্দাবনদাস রচিত ‘চৈতন্যভাগবত’ গ্রন্থটিই চৈতন্যজীবনীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে বিবেচিত হয়ে থাকে ।
চৈতন্যচরিতামৃত : যাঁরা নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বিষয়েও জিজ্ঞাসু তাদের নিকট কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থটিই সর্বাধিক মূল্যবান বিবেচিত হয়। কবিরাজ গোস্বামী প্রত্যক্ষভাবে বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীদের সাহচর্যে এসে তাঁদের আদেশ নির্দেশ শিরোধার্য করেই গ্রন্থটি রচনা করেন।গ্রন্থে প্রদত্ত পুস্তিকা অনুযায়ী গ্রন্থরচনাকাল ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দ কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় গ্রন্থটি অনেক পূর্বেই রচিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা এই তিনখণ্ডে বিভক্ত। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যজীবনের যে সমস্ত কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন, কবিরাজ গোস্বামী পূর্বসূরীর প্রতি সম্মান
প্রদর্শনহেতু ওই সমস্ত অংশ অতি সংক্ষেপে সেরে চৈতন্যদেবের শেষ-জীবনকাহিনী বিস্তৃতভাবে পরিবেশন করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি চৈতন্যদেবের তিরোধান ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন।কবিরাজ গোস্বামী ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত মনীষী, তিনি চৈতন্যজীবনী বর্ণনা অপেক্ষাও অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনের বিভিন্ন তত্ত্ব উপস্থাপনা ও ব্যাখ্যায়। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে কয়েক শো শ্লোক উদ্ধার করেছেন। তাঁর স্বরচিত শ্লোকের সংখ্যাও শতাধিক। বস্তুত বৈদগ্ধ্যে ও মননশীলতায় সমগ্র মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের কোনো দোসর নেই। তাঁর গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে পদ্যে রচিত ধর্ম দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ সাহিত্য।
চৈতন্যমঙ্গল : লোচনদাস এবং জয়ানন্দ উভয়ই ‘চৈতন্যমঙ্গল’ নামে চৈতন্যজীবনী রচনা করেন। লোচনদাস বৃন্দাবনদাসের পরবর্তীকালে বর্তমান ছিলেন। তিনি মোটামুটিভাবে মঙ্গলকাব্যের ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা রচনা করে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। জয়ানন্দও একই পথের পথিক, তিনি অধিকন্তু অনেক পৌরাণিক কাহিনীও এতে যুক্ত করেছেন। লোচনদাস মুরারি গুপ্তের অনুসরণ করেছেন এবং অন্ত্যখণ্ডটি ‘অসম্পূর্ণ রেখেছেন। ‘গৌরপারম্যবাদ’ বা ‘নদীয়া- নাগরবাদে’র প্রবক্তা নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য লোচনদাসও গৌরাঙ্গলীলাকে কৃষ্ণলীলার অনুকরণে সাজিয়ে নদীয়ার কুলবধূদের কামোন্মত্তরূপে বর্ণনা করেছেন। বস্তুত লোচনদাসের কাব্য পলবিত কবিতাংশে অতিশয় উপাদেয় হলেও এতে ঐতিহাসিকতার পরিচয় নেই, এটি আগাগোড়া চমৎকার একটি রোমান্টিক কাব্যে পরিণত হয়েছে। নয়খণ্ডে জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গলে’র কাহিনীতে নানাদিক থেকেই যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি মূলত ছিলেন গায়েন, পালাগানের আকারে কাব্যটি রচনা করেছেন। একমাত্র এঁর গ্রন্থেই চৈতন্যদেবের মহাপ্রয়াণ কাহিনী বিশ্বাসযোগ্যভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে অলৌকিকত্ব না থাকাতেই হয়তো বৈষ্ণবমহলে গ্রন্থটি তেমন সমাদর লাভ করেনি। তবে গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকৃতিলাভের যোগ্য।
গৌরাঙ্গ বিজয় : ‘গোবিন্দদাসের কড়চা’ নামে যে চৈতন্যজীবনীটি প্রচারিত হয়েছে, এর প্রামাণিক্তায় যথেষ্ট সংশয়ের কারণ রয়েছে। একমাত্র জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ গোবিন্দ কর্মকার নামক এক চৈতন্যসঙ্গীত উল্লেখ পাওয়া যায়, অন্যত্র কোথাও এর সন্ধান পাওয়া যায় না। গ্রন্থে গোবিন্দ কর্মকার নিজেকে ‘হাতা-বেড়ি-গড়া’ ‘নির্গুণ মূর্খ’ কর্মকার বলে উল্লেখ করেও যেভাবে বিভিন্ন বৈষ্ণব তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন এবং ইংরেজি ও পর্তুগিজ আমলের বস্তু বা স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন, তাতে পণ্ডিতগণ এটিকে প্রামাণিক গ্রন্থের মর্যাদা দান করেননি। চূড়ামণি দাস রচিত ‘গৌরাঙ্গ-বিজয়’ নামক একটি চৈতন্যজীবনী খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে। এতে কোনো পরিচ্ছেদ বিভাগ নেই। গ্রন্থকার চৈতন্যদেবকে ‘অবতার’ বলে বিশ্বাস করলেও বাস্তবতাবোধের পরিচয় রেখেছেন সর্বত্র। গ্রন্থটি সম্ভবত ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই রচিত হয়েছিল। এ ছাড়া জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ কাব্যে পূর্ববর্তী কয়েকটি চৈতন্যজীবনীর উল্লেখ আছে, কিন্তু গ্রন্থগুলোর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। এদের মধ্যে আছে-গৌরীদাস পণ্ডিত রচিত একটি গ্রন্থ, পরমানন্দ কৃত ‘গৌরাঙ্গ বিজয়’ এবং গোপাল বসু রচিত ‘চৈতন্যমঙ্গল’।
উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, মহাপুরুষের জীবনকাহিনী অলম্বনে যে চরিত সাহিত্য রচিত হয়েছে তা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অন্যরকম এক ধারা শুধু তাই নয়, মধ্যযুগের বংলা সাহিত্যকেও একধাপ এগিয়ে দিয়েছে এ চরিত সাহিত্য। তাছাড়া এ সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বিষয়ের সাথে একরণের বৈচিত্র্য।
শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বাঙালির ও বাংলাসাহিত্যের রেনেসাঁসের যুগ-আলোচনা করো।
পরবর্তী পরীক্ষার রকেট স্পেশাল সাজেশন পেতে হোয়াটস্যাপ করুন: 01979786079
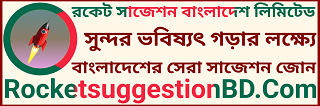
Leave a Reply