অথবা, ‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’ অবলম্বনে কাজী নজরুল ইসলামের সংগ্রামী চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।
উত্তর৷ ভূমিকা : দুঃখ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর হৃদয়ে ন্যায়-সত্য সাম্য ও সুন্দরের অবিনাশী বাণী ধারণ করে নিজ কবি মানস নির্মাণে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এ কারণেই তাঁর লেখায় অসত্য, অন্যায় ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে দর্পিত প্রতিবাদ এবং জ্বলন্ত বিদ্রোহের গর্বিত উচ্চারণ স্থান পেয়েছে। আলোচ্য ‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’ প্রবন্ধেও সে কবিমানসের পরিচয় বিধৃত রয়েছে।
কবিমানস : ‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’ প্রবন্ধ হলেও শব্দচয়ন, বুনন, ছন্দ এবং কাব্যরসে এটি একটি কাব্যধর্মী প্রবন্ধ । আবেগ, যুক্তি, প্রতিবাদী শব্দবিন্যাস ও বাক্যের কাঠমো নির্মাণে এটি উত্তেজনা ও অনুপ্রেরণার উৎসমূলক প্রবন্ধ। এর উৎসস্থল কবির অন্তর, কবির কবিসত্তা কবির আত্মা। এ আত্মা বিদ্রোহী এবং অবিনাশী। এর নির্মাতা এবং উৎসাহদাতা স্বয়ং ভগবান। কবির এ দেশপ্রেম মানবপ্রেম ও স্বাধীনতা কামনায় সমুজ্জ্বল ।
কারাবরণের প্রেক্ষাপট : পরাধীন ভারতের মুক্তি আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সাহিত্য সাধনার পাশাপাশি কবি ‘ধূমকেতু’ নামে একটি অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর সম্পাদিত এ পত্রিকায় জ্বালাময়ী ও বিপ্লবাত্মক কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকলে কবি রাজরোষের কবলে পড়েন। রাজশক্তি বিরোধী এসব প্রকাশনার কারণে রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।
তিন ধূমকেতুর প্রতীক : পরাধীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার ভারতবর্ষের মানুষ সে সময় ছিল স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ নিবেদিত প্রাণ । সে যুগের উত্তাপ ও উত্তেজনা প্রতিফলিত হয়েছিল ‘ধূমকেতু’তে। ফলে এটা শুধু আপামর জনতার মধ্যে আলোড়নই সৃষ্টি করেনি, সকল মহলের হৃদয়ও জয় করেছিল। এর মূলে ছিল যুগোপযোগী আবেগ উত্তেজনাময় কাব্যিক উপস্থাপনা। আর ছিল কবির আত্মোপলব্ধির আত্মবিশ্বাসের চেতনালব্ধ সহজ সত্যের সরল স্বীকারোক্তি
সংগ্রামী চেতনা : পৃথিবীর দেশে দেশে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে তীব্র সংগ্রাম। কিছু দেশ তুখোড় আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তার কাঙ্ক্ষিত জোয়ারের প্রচণ্ড ঢেউ এসে লেগেছে এদেশের মানুষের সত্তায়। কবি সাহিত্যিকরা অবিরাম লিখে যাচ্ছেন চূড়ান্ত মুক্তি লক্ষ্যে। কাজী নজরুল ইসলাম শুধু পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার উদ্দেশ্যে গণজাগরণই সৃষ্টি করেননি, তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় কর্মী, নেতা এবং দ্রষ্টা। তাঁর কাব্য সাধনার মূলে যে বিষয়টি ক্রিয়াশীল ছিল তা হলো বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ মিথ্যার বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, প্রতারণার বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে, অন্ধবিশ্বাস ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে। অলস, ভীরু, অকর্মণ্য জীবন এবং জরাজীর্ণ ও অকল্যাণকর রীতিনীতির বিরুদ্ধে ছিল তাঁর আজীবন বিদ্রোহ্। এগুলোই এ উপমহাদেশের ক্ষয়িষ্ণুতার কারণ, উন্নতি ও অগ্রগতির প্রতিবন্ধকতা। উদার, মহৎ ও কল্যাণকামী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী কবি মানবিক মূল্যবোধের উজ্জীবনের মাধ্যমে এদেশকে মহামিলনের উন্নত প্রতীক হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁর কবিমানসের ভিত্তি এর উপরই বিকশিত হয়েছে। সত্য, ন্যায়, সাম্য ও শান্তি ছিল সে ভিত্তির আদর্শ। এজন্যই নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছেন- “আমি সত্য প্রকাশের যন্ত্র।”
পরম আত্মবিশ্বাস : পরম আত্মবিশ্বাসী কবি তাঁর বিবেক শক্তির বিচারে যা কিছু মিথ্যা, অন্যায় মনে করেছেন তাকে অকপটে মিথ্যা ও অন্যায় বলেছেন। তিনি কারো তোষামোদ করেননি, প্রশংসা এবং স্বার্থের লোভে কারো লেজ ধরেননি। তাতে তাঁর আত্মোপলব্ধির প্রতি অবিচার হতো, আত্মপ্রসাদকে খাটো করা হতো, ব্যক্তিত্বকে অপমান করা হতো। তিনি সত্যের হাতের বীণা। সুতরাং, নিজের কাছে নিজেকে অভিযুক্ত ও হীন করতে পারেন না। এ জন্যই স্বচ্ছন্দে বলেছেন, “আমি অন্ধ বিশ্বাসে, লাভের লোভে, রাজভয় বা লোক ভয়ে মিথ্যাকে স্বীকার করতে পারিনি।”
বিশ্লেষণ ক্ষমতা : পরিবেশ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সত্য ও সুন্দরকে বের করে আনার ক্ষমতা কবির ছিল। জনগণের স্বার্থে জনগণের জন্য যা কিছু উৎকৃষ্ট, কবির লেখনীতে তা-ই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠেছে কাল ভৈরবের প্রলয় তূর্য, দুলে উঠেছে তাঁর হাতের ধূমকেতুর অগ্নিনিশান। আর তা তীব্র আবেগে সঞ্চারিত হয়েছে জনতার অন্তরের সুগভীর চেতনায়। সে উত্তাল দিনগুলোতে তিনি বুঝেছিলেন, “আমি সত্য রক্ষার, ন্যায় উদ্ভাবের বিশ্ব প্রলয় বাহিনীর লাল সৈনিক।”
সত্যদ্রষ্টা : কবির আত্মা ছিল সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা- যা তাঁর রাজকারাগারের সশ্রম বন্দী জীবনকেও অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি কোন কিছুতেই ভয় পাননি, ভেঙে পড়েননি, আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। বরং তা তাঁর দৃষ্টিকে আরো গভীর করেছে; তাঁর শক্তি, সাহস ও মনোবলকে সুদৃঢ় করেছে। এদেশের মানুষের উপর অত্যাচার, পীড়ন, লাঞ্ছনা ও অপমানের বিচিত্র কৌশল ও নির্মম প্রকৃতি দেখে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন, “আমার হাতের ধূমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নিমশাল হয়ে অন্যায় অত্যাচারকে দগ্ধ করবে।”
উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার পেক্ষিতে বলা যায় যে, সত্য এবং ন্যায় অনুশীলনের মধ্যেই কল্যাণ, সাম্য এবং সুন্দরের চর্চার মধ্যেই শান্তি ও সুখ। কবি কায়মন বাক্যে এসবের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই তাঁর কবি মানসকে নির্মাণ করেছেন, উৎসর্গ করেছেন। তাঁর বাণী প্রকাশ করেছেন মানুষ ও সমাজের সামগ্রিক কল্যাণে। তাই কবির কণ্ঠে প্রকাশ পায়-
“ঐ অত্যাচারীর সত্য পীড়ন
আছে তার আছে ক্ষয়,
সে সত্য আমার ভাগ্য বিধাতা
যার হাতে শুধু রয়।”
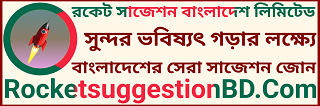
Leave a Reply