অথবা, কাজী নজরুল ইসলাম কীভাবে তাঁর বিদ্রোহী সত্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, ‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’ প্রবন্ধ অবলম্বনে তা তুলে ধর।
উত্তর৷ ভূমিকা : বিদ্রোহী সত্তার অধিকারী কাজী নজরুল ইসলাম বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সূচনা করেছিলেন। তাঁর ওজস্বী সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে তিনি তীক্ষ্ণ লেখনী ধারণ করে তাদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। এ কারণে ‘ধূমকেতু মামলায়’ রাজদ্রোহের অভিযোগে কবিকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়। এ সময় আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করে তিনি যে জবানবন্দী প্রদান করেন, তা কবির ‘বিদ্রোহী আত্মার মূর্ত প্রতীক’ হিসেবে পরিগণিত।
বিদ্রোহীর স্বরূপ : বিচার-বিশ্লেষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে, ন্যায় এবং সত্য সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কোন কল্যাণকামী ব্যক্তিত্ব, কোন দেশপ্রেমিক বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হন না। এ বিদ্রোহের কারণ মূলত মানবতা বা মানবাত্মার অবমাননা। যাঁরা মানুষের সমানাধিকার এবং সমমর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাঁরা এর অবনতি, অপমান বা অপপ্রয়োগ দেখলেই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেন। মানুষ হিসেবে অন্যকে সচেতন করার জন্য তাঁরা সক্রিয়ভাবে তৎপর হয়ে উঠেন। নিজের প্রতি, নিজের লাভ-লোকসানের প্রতি, এমনকি নিজের জীবনের ঝুঁকির মুখেও তাঁরা বিরত হন না। এমনি একজন কিংবদন্তী বিদ্রোহী হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। গানে, বক্তৃতায়, প্রতিটি লেখায়ই তাঁর বিদ্রোহের স্পর্শ। ‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’ প্রবন্ধেও তাঁর বিদ্রোহী আত্মার মূর্ত প্রকাশ ঘটেছে।
রাজদ্রোহী কবি : একজন রাজা, তাঁর হাতে রাজদণ্ড। রাজশক্তিরও তিনি মধ্যমণি। তাঁর বিরুদ্ধে কেউ বিদ্রোহ করলে তিনি শাস্তি দিতেই পারেন। কিন্তু বিদ্রোহটা যৌক্তিক কি না, জনকল্যাণকর কি না, গঠনমূলক কি না সে বিষয়ে সম্যক অবগত না হয়ে রাজদ্রোহী বলাটা কতটা যুক্তিযুক্ত? নিশ্চয়ই রাজশক্তি তা ভেবে দেখেনি। শুধু ক্ষমতার দাম্ভিকতা প্রকাশের মাধ্যমে জনরোষকে চাপা দেয়ার জন্যই কবিকে কারাবন্দী করা হয়েছে। এটা অবশ্যই জনবিরোধী ষড়যন্ত্র। অর্ধ সাপ্তাহিক ‘ধূমকেতু’ পত্রিকায় রাজশক্তির অন্যায় অত্যাচারের সমালোচনামূলক কবিতা প্রবন্ধ লেখার কারণেই তাঁকে কারাভ্যন্তরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কবি এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাই নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছেন, “একধারে রাজমুকুট; আর ধারে ধূমকেতুর শিখা।”
অপ্রকাশ্যের প্রকাশক : কবি নিশ্চিত যে তিনি কোন অন্যায় করেননি। তিনি গণমানুষের প্রতি তাঁর পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছেন। যে অপ্রকাশ্য কথাগুলো বলতে সবাই ভয় পেয়েছে, তিনি তা নির্ভয়ে দৃঢ়তার সাথে প্রকাশ করে দিয়েছেন। রাজার কর্মকাণ্ডের ভাণ্ডারে যা কিছু অমূর্ত ছিল তিনি সেগুলো মূর্তিময় করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, “আমি কবি, অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তি দানের জন্য ভগবানকর্তৃক প্রেরিত।”
কবি সত্যদ্ৰোহী : কবির বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে। কিন্তু কবি জানেন, তা ন্যায়বিচারে ন্যায়দ্রোহী নয়, সত্য বিচারে সত্যদ্রোহী নয়। স্পষ্টবাদী কবি বাস্তবতাকে পাশ কাটিয়ে চলতে পছন্দ করেন না। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বুঝার ক্ষমতা তাঁকে স্রষ্টা দিয়েছেন। তাই কোন ভণিতা না করে বলেছেন, “যা অন্যায় বলে বুঝেছি, তাকে অন্যায় বলেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি….।”
কবির বিদ্রোহী আত্মা : সত্য উচ্চারণ যদি বিদ্রোহ হয় তাহলে তিনি বিদ্রোহী। ন্যায় ও সুন্দরকে অনুসরণ যদি বিদ্রোহ হয় তাহলে তিনি জাত বিদ্রোহী। এ বিদ্রোহ তাঁর সহজাত, এর বিপুল শক্তি ভগবানের কাছ থেকে পাওয়া। তাঁর মনে-প্রাণে এ বিদ্রোহ, তাঁর অন্তর জুড়ে এ বিদ্রোহ, এ বিদ্রোহ তাঁর আত্মার মধ্যে নিহিত। তাই লোভ দেখিয়ে কেউ তাঁকে আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি, ভয় দেখিয়ে কেউ তাঁকে সে পথ থেকে সরাতে পারেনি। কেননা তিনি, “উৎপীড়িত আর্ত বিশ্ববাসীর পক্ষে সত্য তরবারি, ভগবানের আঁখিজল।”
প্রতিবাদী : ব্রিটিশ রাজশক্তি দাসকে সেবক প্রকারান্তরে গোলাম বলেই মনে করতো। যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এদেশের সাধারণ মানুষকে দেখত সে হীন মনমানসিকতা নিয়েই এদেশের অসচেতন মানুষের সাথে রূঢ় ও নির্মম আচরণ করতো তারা। কেবল কবি একথাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেই দোষ। তাদের ভুল ধরিয়ে দিয়ে তার কঠোর সমালোচনা করলেই অপরাধ। আর এ বিষয়টা জনগণের কাছে উপস্থাপন করে তাদেরকে সচেতন করতে গেলেই সেটা রাজদ্রোহ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, “দাসকে দাস বললে অন্যায়কে অন্যায় বললে এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ।” ন্যায় এবং সত্যকে মানুষ অনুধাবন করেছে, আজ সত্য জেগে উঠেছে। জেল-জুলুম, অত্যাচার নিপীড়ন করেও সে সত্যকে ধামাচাপা দেওয়া যাবে না। মাঠে-ময়দানে, রাজপথে জাগ্রত মানুষের গগনবিদারী প্রতিবাদের আওয়াজ। সে সাথে বঞ্চিত, নির্যাতিত মানুষের বুকফাটা হাহাকার। এ অবস্থায় কবির প্রশ্ন, “এই অন্যায় শাসনক্লিষ্ট বন্দী সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল। বলেই কি আমি রাজদ্রোহী?” কবিকে বন্দী করলে যেমন সচেতন মানুষের আন্দোলন বন্ধ হবে না, তেমনি কবির ‘ধূমকেতু’ বাক্সবন্দী করলেই কবির কণ্ঠ স্তব্ধ হবে না। কেউ না কেউ নতুন ‘ধূমকেতু’ প্রকাশ করবে, কারো না কারো কণ্ঠে বিদ্রোহের বাণী ফুটে উঠবে। এ প্রসঙ্গে কবির উক্তি, “আমার এ শাসন নিরুদ্ধ বাণী আবার অন্যের কণ্ঠে ফুটে উঠবে। আমার হাতের বাঁশি কেড়ে নিলেই সে বাঁশির সুরের মৃত্যু হবে না।”
উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার পেক্ষিতে বলা যায় যে, কবি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেননি, সমাজের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, শ্রেণিভেদের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করেছেন। বিদ্রোহ করেছেন সামন্তবাদী মহাজনী মনোভাব যারা পোষণ করে, সেসব স্বার্থান্ধ শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেও। জাতীয় জীবনে যারা মিথ্যাবাদী, প্রতারক, বিদ্বেষী তাদের বিরুদ্ধেও কবির বিদ্রোহ। তাঁর কাছে আপামর মানুষের কল্যাণ স্বার্থটাই বড়, দেশ ও জাতির গঠনমূলক উন্নয়ন ও অগ্রগতিটাই বড়। সামান্য সংখ্যক মানুষের ব্যক্তি স্বার্থের জন্য তিনি তা জলাঞ্জলি দিতে পারেন না। এখানেই তাঁর বিদ্রোহের মাহাত্ম্য।
রাজবন্দীর জবানবন্দী’ প্রাবন্ধিক কাজী নজরুল ইসলামের ‘বিদ্রোহী আত্মার মূর্ত প্রতীক’- এ উক্তির আলোকে বিদ্রোহের মাহাত্ম্য বর্ণনা কর।
পরবর্তী পরীক্ষার রকেট স্পেশাল সাজেশন পেতে হোয়াটস্যাপ করুন: 01979786079
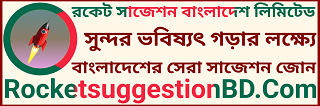
Leave a Reply