অথবা, ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কাকে অপরাধ বলে গণ্য করেছেন- তা বিস্তৃত আলোচনা কর।
উত্তর ভূমিকা : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আশিতম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে পাঠ করার উদ্দেশ্যে ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনি সাম্প্রতিক অতীতের চিন্তাচেতনার হিসাব কষে ব্যক্তিগত উপলব্ধির সমালোচনা করেছেন নিবন্ধটিতে। পাশ্চাত্য সভ্যতার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একদিকে তিনি যেমন হতাশ হয়েছেন, অন্যদিকে স্বদেশের উপর বিশ্বাস না হারিয়ে অনাগত ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। কবির সে আশাবাদ বৃথা যায়নি। বর্তমান ভারতবর্ষই তার প্রমাণ। ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনে ইংরেজ ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছে। মনুষ্যত্বের বিজয়বার্তা ঘোষিত হয়েছে।
পাশ্চাত্য সভ্যতা : পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলে ছিল মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য-সংস্কৃতির আলোকে নিজেদের আলোকিত করে বিশ্বমানবতাবাদের অমর বাণী তারা প্রচার করেছিল পৃথিবীর দেশে দেশে। তখনকার দিনরাত্রি মুখরিত ছিল বার্কের বাগ্মিতায়, মেকলের ভাষা প্রবাহের তরঙ্গভঙ্গে, শেক্সপিয়ার ও বায়রনের সাহিত্যচর্চার উৎকর্ষতায় এবং এন্ড্রুজের মানবতাবাদী অভিভাষণে। ইংরেজ জাতির মহত্ত্বকে এরা সকল প্রকার নৌকাডুবির হাত থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা রাখতেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী হিংস্র লোলুপতার কারণে ইংরেজ সভ্যতা তার মূল সুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতা তার ভেতরকার নিজস্ব সম্পদ মানবতাবাদী বৈশিষ্ট্যকে হারাল। রাজনৈতিক শাসন শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হলো সভ্যতার সকল ধরনের মহত্ত্ব। ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ মানবমৈত্রীর বাহুবন্ধন থেকে ছিন্ন হয়ে গেল। অথচ সেদিন কী গ্রহণযোগ্যতা সে অর্জন করেছিল ভারতবর্ষে! এক সময় নিজ দোষে সে একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।
সভ্যতার নগ্নরূপ : জীবনের শেষপ্রান্তে এসে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যহ দেখতে পেলেন সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিত রূপে স্বীকার করেছিল রিপুর তাড়নায় তারা তাকে অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে। ইংরেজ শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট ভারতবাসীর দারিদ্র্যের যে নিদারুণ ছবি তিনি প্রত্যক্ষ করলেন তা হৃদয়বিদারক। অন্ন-বস্ত্র-পানীয়-শিক্ষা-চিকিৎসা প্রভৃতি যা কিছু মানুষের দেহমনের জন্য অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসনচালিত কোন দেশেই ঘটেনি। অথচ এ হতভাগ্য দেশ দীর্ঘকাল ধরে ইংরেজকে ঐশ্বর্য যুগিয়ে এসেছে। কবি যখন সভ্যজগতের মহিমাধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন তখন ভুলেও সভ্য নামধারী মানব আদর্শের এতবড় নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারেননি। এক সময় তিনি যাদেরকে হৃদয়ের উচ্চাসন বসিয়েছিলেন তাদের মেকি সভ্যতার নগ্নরূপ দর্শনমাত্রই তাদেরকে পরিত্যাগ করতে দ্বিধা করেননি।
ইংরেজ শাসনের প্রবঞ্চনা : ইংরেজরা মানবতাবাদের পৃষ্ঠপোষক ও প্রচারক হলেও ভারতবর্ষে তারা মানুষের সাথে প্রবঞ্চনা করেছে। তাদের শাসনের মধ্যে বিশ্বমানবতাবাদের মহান বাণী ছিল একেবারেই অনুপস্থিত। যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে তার যথোচিত চর্চা থেকে এ নিঃসহায় দেশকে করেছে বঞ্চিত। অথচ জাপান, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ এ যন্ত্রশক্তির সাহায্যে নিজেদের সমৃদ্ধ করেছে। ইংরেজরা ভারতীয়দের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে চিরকালের মতো নির্জীব করে রাখতে চেয়েছিল। ইরান এ ইউরোপীয় জাতির চক্রান্তজাল থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল বলেই তাদের দেশে সভ্য শাসনের বিস্তার ঘটেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তাদের চক্রান্ত বুঝতে না পারার কারণে ইংরেজের সভ্য শাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে অতলতলে তলিয়ে রইল। সভ্য শাসনের চালনায় ভারতবর্ষে সবকিছুর চেয়ে যে দুর্গতি সেদিন মাথা তুলে উঠেছিল তা বৈষয়িক দারিদ্র্য নয়- তা ভারতীয় জাতিসত্তার মধ্যে ইংরেজ আরোপিত অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ। অত্যন্ত সুকৌশলে তারা ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিজাতি তত্ত্বের বিষবৃক্ষ রোপণ করে বিষফলের উৎপাদন নিশ্চিত করেছিল।
ইংরেজ শাসনের কৌশল : ভারতীয়রা বুদ্ধিসামর্থ্যে কোন অংশে কম না হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজ শাসনের কৌশলগত শোষণে জাপানিদের চেয়ে অনেক পিছনে পড়ে রইল। এ দুই প্রাচ্য দেশের সর্বপ্রধান প্রভেদ এই, ইংরেজ শাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ছিল ভারত, আর জাপান এরূপ কোন পাশ্চাত্য জাতির পক্ষছায়ার আবরণ থেকে ছিল মুক্ত ও স্বাধীন। ইংরেজরা ‘Law and order’ এর কৌশলের সাহায্যে ভারতীয়দের করে রেখেছিল পদানত। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা তাই লেখকের পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠেছিল। ইংরেজ তার শক্তিরূপ ভারতীয়দের দেখিয়েছে, কিন্তু মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সবচেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে, কৌশলে তা থেকে আমাদের বঞ্চিত রেখে উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে রেখেছিল।
প্রাবন্ধিকের আশাবাদ : ভারতীয়দের দুরবস্থা দেখে রবীন্দ্রনাথ হতাশ হলেও আশা ছাড়েননি। তাঁর বিশ্বাস ছিল ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যেতে হবে। তিনি বলেছেন, “আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এ দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে। একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়ত আরম্ভ হবে এ পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহত্মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।” তিনি এও বলেছেন যে, প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তার প্রমাণ হওয়ার দিন আর বেশি দূরে নয়।
উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার পেক্ষিতে বলা যায় যে, ইংরেজ শাসনের নেতিবাচকতায় রবীন্দ্রনাথ হতাশ ও ক্ষুব্ধ হলেও ভারতীয়দের উপর থেকে তিনি বিশ্বাস হারাননি। তিনি আশা করেছেন, ইংরেজ একদিন ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। কারণ কোনকিছুই অন্তহীন ও প্রতিকারহীন নয়। রবীন্দ্রনাথের আশাবাদ বিফলে যায়নি।
মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ বলে মনে করি”- এ উক্তির আলোকে রবীন্দ্রনাথ যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তা নিজের ভাষায় আলোচনা কর।
পরবর্তী পরীক্ষার রকেট স্পেশাল সাজেশন পেতে হোয়াটস্যাপ করুন: 01979786079
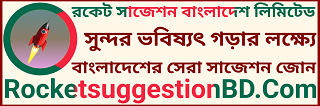
Leave a Reply