অথবা, বৈষ্ণব দর্শন কী? বৈষ্ণব দর্শনে শ্রীচৈতন্যদেবের অবদানগুলো লিখ।
অথবা, বৈষ্ণব দর্শনের সংজ্ঞা দাও। বৈষ্ণব দর্শনে শ্রীচৈতন্যদেবের কী কী অবদান রয়েছে?
উত্তর।৷ ভূমিকা : মধ্যযুগের বাঙালির ধর্ম ও মনন সাধনার ক্ষেত্রে যে মতধারার প্রভাব ছিল সর্বব্যাপ্ততা হলো বৈষ্ণববাদ বা বৈষ্ণব দর্শন। মধ্যযুগের বাংলার মরমিবাদের ঊষর ভূমিতে যে কয়টি দার্শনিক ও ধর্মীয় চিন্তাধারা উদ্ভব ও বিকাশ লাভ করে তন্মধ্যে বৈষ্ণব দর্শন অন্যতম। বৈষ্ণব ধর্মমতের সার ও তত্ত্বকথা নিয়েই গড়ে উঠেছে বৈষ্ণব দর্শন। বৈষ্ণব দর্শন মতধারা মূলত দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। একটি হচ্ছে চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণব দর্শন ধারা এবং অপরটি চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব দর্শন ধারা। বাংলায় বৈষ্ণব দর্শন বলতে আমরা মূলত চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব দর্শন ধারাকেই বুঝি।
বৈষ্ণব দর্শন : বৈষ্ণব ধর্মমতের সার বা নিগূঢ় তত্ত্বকথা নিয়েই গড়ে উঠেছে বৈষ্ণব দর্শন। অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব,ভক্তি আশ্রিত রসতত্ত্ব ও সাহিত্যে বিবৃত নিগূঢ় তত্ত্ব কথার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে বৈষ্ণব দর্শন তত্ত্বে। বৈষ্ণব দর্শনের মূল কথা প্রেমভক্তি করুণা। বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান অনুষ্ঠান শ্রীবিষ্ণুর নামকীর্তন বা উপাসনা। আর এ উপাসনার মধ্যে বিধৃত বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের সার কথা। বিষ্ণুর উপাসনা বিষয়ক সবচেয়ে প্রাচীন দলিল ঋগ্বেদ সংহিতা আর তাতেই ব্যাখ্যাত হয়েছে বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের মূলরূপ ও বৈশিষ্ট্য। তাই বিষ্ণুর উপাসকরাই হলেন বৈষ্ণব। বাংলায় এ মতের উদ্ভব হওয়ার বহুপূর্বে বৈষ্ণব মতের উদ্ভব হলেও এদেশে বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের ভিত্তি প্রথম রচনা করেন রামানুজ তাঁর বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদে। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ছিল জ্ঞানমুখী ও প্রেমভক্তিবাদ বিরোধী। এ নির্জলা অদ্বৈতবাদের প্রভাবে প্রেমভক্তিবাদ হারিয়ে ফেলেছিল তার প্রাণশক্তি তাতেই নবপ্রাণের সঞ্চার করেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ। আর এই মর্তবাদই প্রেমধর্ম বা ভক্তিধর্মরূপে বাংলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের হাতে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানগুরু সক্রেটিস যেমন তেমনি শ্রীচৈতন্যও কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। সংস্কৃত ভাষায় বর্ণিত মাত্র আটটি শ্লোকের মাধ্যমে তিনি জয়গান করেন তাঁর ভক্তিবাদ বা প্রেমাত্মক দর্শনের। তাঁর বর্ণিত এ দর্শনই মধ্যযুগীয় বাঙালি দর্শনের ইতিহাসে বৈষ্ণব দর্শন বা বৈষ্ণববাদ নামে পরিচিতি লাভ করে। শ্রীচৈতন্যের এ প্রেমভক্তিবাদ আশ্রিত ধর্ম ও দর্শনকে কেন্দ্র করেই রচিত হয় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যধারা “শ্রীচৈতন্য জীবনীকাব্য” ও “বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্য”। এসব সাহিত্যেই কাব্যিক আঙ্গিকে বিধৃত রয়েছে বৈষ্ণববাদের দর্শন তত্ত্বকথা।
বৈষ্ণব দর্শনে ‘ শ্রীচেতন্যদেবের অবদান : বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীচৈতন্যদেব। মধ্যযুগের বাংলায়
বিকশিত বৈষ্ণব দর্শন বলতে আমরা শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব দর্শনকেই বুঝি। তাঁর প্রবর্তিত বৈষ্ণব দর্শন গৌড়ীয় বৈষ্ণব
দর্শন নামেই সমধিক পরিচিত। অনেক পণ্ডিতের মতে, শ্রীচৈতন্যের পূর্বেও বাংলায় বৈষ্ণববাদ প্রচলিত ছিল। পঞ্চম শতকে গুপ্ত রাজাদের আমল হতে একপ্রকার বিষ্ণু বা কৃষ্ণতত্ত্ব অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্টভাবে প্রচলিত ছিল। এসময় বাংলায় প্রচলিত বেষ্ণববাদ অবতারবাদের একটি সুশৃঙ্খল রূপ প্রদান করে। কেননা চৈতন্যপূর্ব বাংলাদেশে প্রচলিত আদি বৈষ্ণববাদ যুক্ত হয়েছিল অবতারবাদের প্রবক্তা নবম শতকের মহান দার্শনিক শহচরাচার্যের ভাবশিষ্য দ্বাদশ শতে শ্রীধর স্বামীর সাথে। তবে একণা সত্য শ্রীচৈতন্যই ছিলেন বাংলায় বৈষ্ণব দর্শনের সার্থক প্রবক্তা। তাঁর অবদানেই বৈষ্ণব দর্শন নব প্রাণ লাভ করে এবং বিকাশের সর্বোচ্চ চূড়ায় উত্তীর্ণ হয়। নিম্নে বৈষ্ণব দর্শনে শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :
১. প্রেমভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা : বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনে শ্রীচৈতন্যদেবের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে তিনি এই মতাদর্শকে প্রেমভক্তিবাদের সর্বাত্মক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণববাদের মূল কথাই হলো প্রেম ঈশ্বর প্রেম। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ঈশ্বর ও আরাধ্য, কিন্তু তিনি প্রেমময়, জ্ঞান বা কর্মে নয় তাকে লাভ করতে হলে তিনি যে ঈশ্বর সে কথা ভুলে তাকে ভালোবাসতে হবে। তাইতো চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব মতে, জ্ঞানে নয়, কর্মে নয়, প্রেমভক্তির মাধ্যমেই কেবল সসীম মানুষের পক্ষে পরম ঐশী প্রেম অর্জন ও উপলব্ধি করা সম্ভব। অবশ্য চৈতন্যপূর্ব যুগেও রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করে ভগবভক্তি ও ঈশ্বর প্রেম এদেশে প্রচলিত ছিল। এর প্রমাণ হচ্ছে জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও
চণ্ডিদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। কিন্তু প্রেমের মহান আদর্শ চৈতন্যের পূর্বে সাত্ত্বিকভাবশূন্য হয়ে পড়েছিল। চৈতন্য মহাপ্রভু এতে ধাণের সঞ্চার করলেন। ফলে চৈতন্য পরবর্তীকালে প্রেম ধর্ম ও প্রেমাত্মক দর্শনকে কেন্দ্র করে যে তত্ত্ব সাহিত্য রচিত হলো টা বাঙালির চিন্তাভাবনা তথা সমগ্র উপমহাদেশীয় জীবনে বয়ে আনল এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন।
২. অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব : শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনের প্রবর্তক। শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত দার্শনিক সিদ্ধান্তের নাম অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ। জীবাত্মা ও জগৎ পরস্পর স্বতন্ত্র। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ সাপেক্ষে ঈশ্বর নির্ভর।তিনি মাধবের ভেদ সম্পর্কিত মতবাদ সমর্থন করেন। ঈশ্বর তাঁর অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা জীব ও জগৎকে ধারণ করেন। প্রলয়ে জীব ও জগৎ ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তিতে লয় হয় এটাই হলো চৈতন্যের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ। শ্রীচৈতন্যের মতে, “পরমতত্ত্বই হরি বা কৃষ্ণ । তিনি হলেন ভগবান অর্থাৎ তিনি ঐশ্বর্যবান। ভগবানের ছয়টি ঐশ্বর্য রয়েছে। যথা : পূর্ণ সৌন্দর্য, পূর্ণ ঐশ্বর্য পূর্ণ বীর্য, পূর্ণ যশ, জ্ঞান এবং পূর্ণ ঐশ্বর্যের তিনি অচিন্ত্য ঐক্য। চৈতন্যের মতানুসারে ঈশ্বর তার ঐশ্বর্য ও বীর্য গুণ দুটি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন এবং তিনি জগদাত্মারূপে এতে অন্তসুতে থাকেন এভাবে একাংশে তিনি জীব ও জগৎ ধারণ করেন।জগৎ ও জীব ঈশ্বরের বিভূতি। তাই জীব প্রেম, অহিংসা এবং বিশ্বপ্রেম ঈশ্বর প্রেমের সমতুল্য। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত এই অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব বৈষ্ণব দর্শনে এক নতুন মাত্রার সংযোজন।
৩. মায়াবাদ খণ্ডন : শ্রীচৈতন্য তাঁর গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে শংকরাচার্যের মায়াবাদের খণ্ডন করেন অত্যন্ত সার্থকতার সাথে। ‘ব্রহ্ম সত্য কিন্তু জগৎ মিথ্যা নয়’ গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদের এই মূল বক্তব্য দ্বারা শ্রীচৈতন্য বেদান্ত ভাষ্য, যা অদ্বৈতবাদ তথা মায়াবাদ নামে বিখ্যাত তাকে খণ্ডন করেন। তিনি মনে করতেন শংকর ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা করেননি। ব্রহ্ম নির্বিশেষ নয়। জগৎ এবং জীবন সত্য। শংকর ব্রহ্মসূত্রের মুখ্য অর্থ ত্যাগ করে গৌণ অর্থ বা লক্ষণার্থের উপর জোর দিয়েছেন। এভাবে শ্রীচৈতন্য মায়াবাদের খণ্ডন করে জগৎ ও জীবকে সত্য এবং ঈশ্বরকে গুণসম্পন্ন পরমতত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে বৈষ্ণববাদের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেন।
৪. মানবতাবাদ : শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণব দর্শনকে মানবতাবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। মধ্যযুগের বাংলায় একপর্যায়ে যখন নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বর্ণভেদের যাঁতাকলে পিষ্ঠ হয়ে মরার উপক্রম হয়েছিল ঠিক সে সময়ে একজন যোগ্য কাণ্ডারি হিসেবে হাল ধরেন শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি এমন দর্শন জনগণের নিকট প্রচার করতে থাকেন যেখানে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ স্বীকার করা হয় না, তিনি মনে করতেন সকল জীবই পরমস্রষ্টা ভগবানের সৃষ্টি। তাই তাঁর সৃষ্ট জীবকে অবহেলা বা অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়। এ যুক্তিতে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ সমান এবং সবাইকে একই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। তাছাড়া এও বিশ্বাস করতেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সব মানুষ, সব জীবে বর্তমান। তাই মানুষের সেবা করা মানে ভগবানেরই সেবা করা। মানবতার এই যে অমরবাণী তিনি প্রচার করলেন তা বৈষ্ণব দর্শনকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেল।
৫. উদারতাবাদ : শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব দর্শনে উদার দৃষ্টিভঙ্গির সংযোজন করেন। তাঁর চিন্তাচেতনায় সংকীর্ণতার কোনো স্থান ছিল না। তাঁর দর্শনের মূল লক্ষ্য ছিল সকল মানুষের মুক্তি এবং তার জন্য যে পথ মানুষের অবলম্বন করা উচিত সে দিক নির্দেশনা দান করা। চৈতন্য তাঁর মতাদর্শ সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ তখনকার সময়ে বিদ্যমান সকল ধর্মের অনুসারীদের জন্য এ দর্শন পাঠ অনুশীলন ও পর্যালোচনার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। তাঁর দর্শনের যুক্তি ও চিন্তাচেতনা এতই অকাট্য ছিল যে, কোনো সংকীর্ণতার মধ্য দিয়ে তা প্রচার করতে হয়নি। বৈষ্ণববাদের এই উদার দৃষ্টিভঙ্গি সবাইকে তখন বিস্মিত করেছিল। কেননা মধ্যযুগের সাধারণ মানুষ ছিল সংকীর্ণ মানসিকতার এবং তাদের সামনে যেসব মতবাদ উপস্থাপন করা হতো তা ছিল তাদের মানসিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু চৈতন্য সেই সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে মানুষকে দিলেন অমৃতের সন্ধান। যার মাধ্যমে মানুষ পেল পরমচেতন সত্তাকে লাভ করার এক সুমসৃণ পথ। আর এই উদারতার কারণেই মধ্যযুগের বাংলায় বৈষ্ণব দর্শনের অগণিত ভক্ত অনুসারীর সমাবেশ ঘটেছিল । এভাবে চৈতন্যদেব উদার দৃষ্টিভঙ্গির সংযোজন ঘটিয়ে বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনকে বলিষ্ঠ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন।
উপসংহার : আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যায়, বৈষ্ণব দর্শনের প্রচার ও বিকাশে শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান ছিল অনন্যসাধারণ । শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনে এনেছিল নবপ্রাণের জোয়ার। তাঁর প্রবর্তিত মতাদর্শ বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনকে নিয়ে গিয়েছিল সাধারণ মানুষের কাছে। তাঁর প্রবর্তিত বৈষ্ণব দর্শন প্রেম ও ভক্তির অনুশীলনের দ্বারা মানুষের মানবধর্ম ও দেবধর্মের পার্থক্য ঘুচিয়ে দিল, হরি ভক্তপরায়ণ চণ্ডাল দ্বিজন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হলো। ধর্মের প্রতীকে মানব মহিমা স্বীকৃত হলো।
বৈষ্ণব দর্শন বলতে কী বুঝায়? বৈষ্ণব দর্শনে শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান আলোচনা কর।
পরবর্তী পরীক্ষার রকেট স্পেশাল সাজেশন পেতে হোয়াটস্যাপ করুন: 01979786079
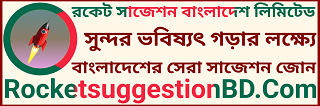
Leave a Reply