অথবা, বাঙালি দার্শনিক হিসেবে লালনশাহের দর্শন তত্ত্ব আলোচনা কর।
অথবা, বাঙালি দার্শনিক হিসেবে লালনশাহের দার্শনিক চিন্তাধারা ব্যাখ্যা কর।
অথবা, বাঙালি দার্শনিক হিসেবে লালনশাহের দর্শন চিন্তা বর্ণনা কর।
অথবা, বাউল সাধক লালন ফকিরের দর্শন-ভাবনা সম্পর্কে যা জান লেখ।
উত্তর।৷ ভূমিকা : লালনশাহ বাংলার লোকদর্শনের প্রাণপুরুষ মধ্যযুগের বাঙালির ভাবান্দোলনের মহানায়ক। মধ্যযুগের বাংলায় বিকশিত যেসব ধর্মীয় ও দার্শনিক ভাবধারা এদেশের মানুষের জীবনাদর্শে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল তন্মধ্যে লালনশাহ প্রচারিত বাউলবাদ ছিল অন্যতম প্রধান। লালন শাহ সাধারণভাবে বাউল সম্রাট হিসেবেই আমাদের নিকট অতি পরিচিত। বাউলধর্ম বা দর্শন বলতে আমরা লালনকেই বুঝি। ঊনিশ শতকে লালন শাহের সাধনা ও গানের মধ্য দিয়েই বাংলায় বাউল মতাদর্শ পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে। এক কথায় লালন শুধু বাউল দর্শনই নয়, বরং তিনি ছিলেন বাঙালি দর্শনের প্রতিভূ পুরুষ।
লালন শাহের দর্শন চিন্তা : বাংলার মরমি সাধক ও বাউলকুল শিরোমণি লালন শাহের জন্ম ১৭৭৪ সালে। বাউল ও বাউল দর্শন বলতে মূলত লালনের জীবনসাধনা ও তাঁর গানকেই বুঝায়। লালন লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে তাঁর জীবনব্যাপ্ত সাধনা দিয়ে বাউল দর্শনের ঐতিহ্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি যদিও বাউল দর্শনের প্রবর্তক বা প্রথম প্রচারক ছিলেন না তথাপি তাঁর কর্মসাধনার মধ্য দিয়েই বাউল দর্শন বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করে। এ প্রসঙ্গে ড. আহমদ শরীফ যথার্থই মন্তব্য করেছেন, “সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় পাদে মুসলমান রমণী মাধববিবির শিষ্য নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্রের হাত ধরেই বাউল দর্শনের যাত্রা শুরু হয় এবং উনিশ শতকে লালন শাহের গানের মাধ্যমে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে।” লালন ছিলেন মূলত একজন স্বভাব কবি। তিনি তাঁর কবি মন দিয়ে দেহতত্ত্ব, আত্মাতত্ত্ব গুরুতত্ত্ব ইত্যাদি জটিল ভাবের গান গেয়ে তাঁর দর্শন চিন্তাকে প্রকাশ করেন। নিম্নে তাঁর দর্শন চিন্তার বিভিন্ন দিক সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।
১. মরমিবাদ : লালন ছিলেন একজন মরমিবাদী দার্শনিক। তাঁর দর্শন চিন্তায় তথা গান ও সাধনায় মরমিবাদের উৎকৃষ্ট বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। আপন হৃদয়ে পরমসত্তাকে অপরোক্ষ অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করার সাধনাই মরমি সাধনা বা মরমিবাদ। লালন তাঁর সমগ্র জীবনকর্ম ও গানে এই উপলব্ধিই করতে চেয়েছেন সর্বান্তকরণে। লালন তাঁর মরমিবাদী চিন্তায় মনের মানুষকে (পরমসত্তাকে) খুঁজে ফিরেছেন এবং সে পথ পরিক্রমায় তিনি ক্লান্ত পরিশ্রান্ত তবু তিনি পথ পাড়ি দিচ্ছেন। মনের মানুষ তথা পরমসত্তার সাথে মিলিত হবার, একাত্ম হবার এই যে আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা লালনের দর্শনে প্রকাশ
পায়, তাই তাঁর মরমি আদর্শকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। লালনের দেহাত্মবাদ, আত্মাতত্ত্ব, পরমাত্মাতত্ত্ব, গুরুবাদ, আত্মতত্ত্ব ইত্যাদি প্রতিটি তত্ত্বেই তাঁর মরমি আদর্শের প্রভাব সুস্পষ্ট।
২. আত্মতত্ত্ব : আত্মতত্ত্ব লালনের দর্শনের মূলতত্ত্ব। এ তত্ত্বের মধ্য দিয়েই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে লালনের মরমি দর্শনাদর্শ। লালনের মতে, মানুষের এসেন্স বা অন্তঃসার তার দেহেই নিহিত। তিনি তাঁর দর্শনে মানবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোনো প্রভেদ করেনি। তিনি বিশ্বাস করতেন দেহ সাধনার মধ্য দিয়েই পরমাত্মার সাধনা করা যায়।দেহের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় পরম স্রষ্টাকে। তাইতো লালন আত্মতত্ত্বের সাধনায় মগ্ন থেকেছেন সারাজীবন। তাই তিনি বলেছেন “মানুষ তত্ত্ব যার সত্য হয় মনে, সে কি অন্য তত্ত্ব মানে।” এই আত্মতত্ত্ব থেকেই লালন প্রেরণা পেয়েছেন মানব সত্তার মূলতত্ত্বে যাবার। তিনি পার্থিব মানব অভ্যন্তরেই আবিষ্কার করেছেন অপার্থিব মানবসত্তা। তাঁর এ আত্মতত্ত্বই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর রচিত গানের নিম্নোক্ত দুটি লাইনে—
“এই মানুষে আছেরে মন
যারে বলে মানুষ রতন।”
আর এই মানুষ রতন বা পরমাত্মার সাথে মানবাত্মার মিলনের প্রচেষ্টাই লালনের হৃদয়ানুভূতিকে ব্যাকুল করে তুলেছিল। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন এ মনের মানুষকে জানলেই নিজেকে জানা যায় পরম সত্তাকে জানা যায়। তাইতো লালন একে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন অন্তরের আলোকে পরোক্ষ অনুভূতির সাহায্যে।
৩. প্রেমভক্তিবাদ : প্রেমভক্তিবাদ লালনের দর্শনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। লালন তাঁর গানে সাধনায় বাড়ির পাশের আরশি নগরের পড়শিরূপী সেই মনের মানুষের সন্ধান করেছেন। আর এই মনের মানুষের সন্ধান তিনি করেছেন ধর্মীয় চেতনার আবরণে, প্রেমভক্তির মাধ্যমে। কেননা লালন এই সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ভক্তি ছাড়া এ জীবন থেকে মুক্তি নেই। তাই তিনি বার বার তাঁর মনে ভক্তি চেয়েছেন কারণ ভক্তিতেই স্রষ্টা জগৎ মুক্তিতে ভুলিয়েছেন। তাইতো লালন বলেন-
“জগৎ মুক্তিতে ভোলালেন সাঁই
ভক্তি দাও যাতে চরণ পাই।”
তাছাড়া বাউল প্রেমতত্ত্বেরও একটি চিত্তাকর্ষ বর্ণনা দিয়েছেন লালন তাঁর দর্শনে। তিনি বলেন “বাউল প্রেমতত্ত্ব রমণী যুবতী বা কামিনীর প্রেম নয়, কিংবা লোভী ও কামী ব্যক্তির পার্থিব ধর্ম, সম্পদ দালানকোঠা, ঘরবাড়ি স্ত্রী-পুত্র পরিবার পরিজন, প্রভাব প্রতিপত্তি, দম্ভ অহংকার ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণ নয়, লোভী, কামী প্রভৃতি শ্রেণির লোকের প্রেমের রাজ্যে অধিকার নেই। এ প্রেম প্রাকৃতিক প্রেম নয় বরং কাম হতে প্রেমে উত্তীর্ণ হওয়ার ঐশ্বরিক প্রেম।” তাই তিনি উপদেশ দিয়েছেন, “পড়া সহজ প্রেম স্কুলে জ্ঞানের উদয় হয়ে যাবে ভুল।” এই প্রেমের সাধনাই বাউল তথা লালনের সাধনা। প্রেমে
তন্ময়তার মধ্য দিয়েই বাউলরা পরমাত্মা বা পরমতত্ত্বের সাথে একাত্ম হতে চান, উপলব্ধি করতে চান। লালন দীর্ঘ জীবনের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে প্রেম সম্পর্কে বলেছেন, “আমি ডুব দিয়ে রূপ দেখলাম প্রেম নদীতে, আল্লাহ আদম ও মুহাম্মদ তিন জনা এক নুরেতে।”
৪. জ্ঞানতত্ত্ব : জ্ঞানের ক্ষেত্রে লালন শাহ স্বজ্ঞা বা দিব্যজ্ঞান তথা মরমি অভিজ্ঞতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিলেও জ্ঞানের উৎস হিসেবে বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা উভয়ের প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। লালনের জ্ঞান আলোচনা সংশয় পদ্ধতি দিয়ে শুরু হয় এবং অভিজ্ঞতাবাদ, বুদ্ধিবাদ প্রেমভক্তি স্বজ্ঞাবাদ প্রভৃতি পদ্ধতির ভিতর দিয়ে দিব্য জ্ঞানলাভের দ্বারা মানবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনের মধ্য দিয়ে এ প্রক্রিয়া শেষ হয়। জ্ঞানলাভের উপায় সম্পর্কে লালন বলেন, “ঈমান বা দৃঢ় বিশ্বাস সত্যের অন্তর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বা মরমি অভিজ্ঞতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়; সত্যের প্রতি প্রেম আকর্ষণ বাড়িয়ে দেয়,
পরমাত্মা ও মানবের মিলনের পথ প্রশস্ত করে এবং সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে দিব্যজ্ঞানের মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞানলাভে সাহায্য করে। তিনি মনে করেন, মানুষের জ্ঞানলাভের বৃত্তি বা শক্তিসমূহের বিচারসাম্য যদি করা হয়, তবে একজন সাধক দিব্যজ্ঞান লাভে সক্ষম হন। তিনি বলেন তবে বিচারসাম্য করা অত্যন্ত কঠিন দিব্যজ্ঞানীই এই বিচারসাম্য বিষয়ে সঠিক জ্ঞান রাখে অন্যে নয়। লালন তাঁর বহুগানে এ দিব্যজ্ঞানের কথা প্রকাশ করে বলেছেন যে, এ দিব্যজ্ঞান তথা স্বভাবজাত জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান যা একদিকে নিম্ন পর্যায়ের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির চাহিদার সাথে অনেকাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং উচ্চপর্যায়ে প্রেমভাব ভক্তি দয়া করুণার সাথে প্রায় অভিন্ন। তবে জ্ঞানী না হলে এসব নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তাঁর ভাষায়” জ্ঞানী না হলে নিগূঢ় তত্ত্ব জানবে না।”
৫. যুক্তিবাদ : লালন একজন মরমি সাধক হলেও তাঁর গান ও সাধনায় যুক্তিবাদকে একেবারে ত্যাগ করেনি। যুক্তিবাদের পথ বেয়ে বস্তুবাদও উঁকি দিয়েছে তাঁর দর্শনে। বলা যায় তিনি বস্তুবাদের জমিনে যুক্তিবাদের বেড়া দিয়ে আত্মবাদের আবাদ করেছেন। লালন একজন ধর্মপ্রচারক তাই তাঁর দর্শনে আধ্যাত্মবাদ অনিবার্য। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন আধুনিকতম মানুষ তাই বস্তুবাদ তাঁর দর্শনে স্বভাব আর তাঁর দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি যুক্তিবাদের আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর বহু গানে এই বাস্তববাদভিত্তিক যুক্তিবাদের সুস্পষ্ট প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই । যেমন –
“না জেনে করণ কারণ
কথায় কি হবে
কথায় যদি ফলে কৃষি
তবে কেন বীজ রোপে
অতএব বলা যায়, লালনের দর্শনে ভক্তি এবং যুক্তিবাদ পাশাপাশি চলেছে। তিনি ভক্তি দিয়েই যুক্তিকে গ্রহণ করেছেন এবং একইভাবে যুক্তি দিয়ে ভক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।
“মানবতাবাদ : ‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই মানবতাবাদের এই অমর বাণীর চরম ও পরম বিকাশ ঘটেছে লালনের চিন্তাদর্শন তথা গান ও সাধনায়। লালন মানুষে মানুষে কখনো ভেদাভেদ জ্ঞান করেন নি। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের ঐক্য, সাম্য, শান্তি ও প্রেমের বাণীই তিনি প্রচার করেছেন তাঁর সাধনায়। মানুষকেই তিনি তাঁর সকল সাধনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ সাধনার মাধ্যমেই নিজেকে জানা যায় এবং নিজেকে জানা ও উপলব্ধি করার মাধ্যমেই পরম সত্তাকে জানা ও উপলব্ধি করা যায়। তাই মানুষ তাঁর নিকট স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ট সৃষ্টি, শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। এ মানুষকে আশ্রয় করেই তার সকল সাধনা। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষই সাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরত্ব লাভ করতে পারে। লালনের এই মানবতাবাদী আদর্শের সুস্পষ্ট প্রকাশ আমরা দেখতে পায় তাঁর গুরুবাদে। যেখানে তিনি দেখান যে, অদেখা কোনো ঈশ্বর নয়, কোনো শাস্ত্র বা তত্ত্ব নয় মানুষ গুরুই মানুষকে পারে পরিপূর্ণতা দান করতে, মানুষ গুরুই পারে এই ভজনহীন মানুষকে ‘ইনসানুল কালেম” বা পরিপূর্ণ মানব বানাতে। লালনের ভাষায়-
“ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠ যার
সর্ব সাধন সিদ্ধ হয় তার।”
উদারতাবাদ : লালনের দর্শনে উদারতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ করা যায়। জাতপাত ধর্ম-বর্ণের বিভেদ লালন মানতেন না। তিনি মানুষকে অখণ্ড সত্তা হিসেবে জানতেন। তিনি মানুষকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয় উদার মন নিয়ে মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখেছেন। তাই ব্রাহ্মণ, চামার, চণ্ডাল, মুচি, হিন্দু, মুসলমান সকলের জন্যই ছিল তাঁর দ্বার উন্মুক্ত। আর তাঁর চিন্তার এই উদারতার কারণেই বাউল দর্শন ও ধর্ম মধ্যযুগের বাংলায় পূর্ণাঙ্গ বিকাশ লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল।
৮. সমন্বয়বাদ : লালনের দর্শন চিন্তায় আমরা সমন্বয়বাদী চিন্তার প্রকাশ দেখতে পাই। কেননা তাঁর দর্শনে মরমিবাদ প্রেমভক্তিবাদ যুক্তিবাদ, বাস্তববাদ ইত্যাদির একটি কার্যকর সমন্বয় ঘটেছে। তবে চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি এসব মতের সমন্বয়ে স্বীয় মতাদর্শকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন সবার উপরে। তাছাড়া লালনের দর্শনে আমরা তৎকালীন বাংলায় প্রভাব বিস্তারকারী বিভিন্ন ধর্ম এবং দর্শনেরও প্রভাব দেখতে পাই। তবে এসব দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হলেও তিনি কখনো স্বীয় আদর্শ থেকে সরে আসেন নি, বরং বলা যায় এসব মতবাদ ও ধর্মের নির্যাসকে গ্রহণ করে তিনি তাঁর দর্শনের ভিতকে আরো মজবুত করেছেন।
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, লালনের দর্শন চিন্তার পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। এত ক্ষুদ্র পরিসরে এর আলোচনা প্রায় অসম্ভব। তবে উপরের আলোচনা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, লালন ছিলেন একজন বড় মাপের দার্শনিক। তাঁর দর্শন ও দার্শনিক সত্তা নিয়ে বাঙালির গর্ব করার মতো অনেক কিছুই আছে। এককথায় বলা যায়, লালন তাঁর অসাম্য দার্শনিক প্রজ্ঞার বদৌলতেই হয়ে উঠতে পেরেছেন বাঙালি দর্শনের প্রবাদপুরুষ।
বাঙালি দার্শনিক হিসেবে লালনশাহের দর্শন চিন্তা বিস্তারিত আলোচনা কর।
পরবর্তী পরীক্ষার রকেট স্পেশাল সাজেশন পেতে হোয়াটস্যাপ করুন: 01979786079
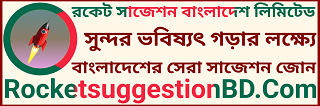
Leave a Reply