অথবা, “নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার নেতিবাচক পরিচয় উদ্ঘাটনই ‘পথ জানা নাই’ গল্পের মূল লক্ষ্য”— আলোচনা কর।
উত্তর : একদিকে অগণিত গ্রাম আর একদিকে স্বল্পসংখ্যক শহর নিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের দেশ। গ্রামের তুলনায় শহরের সংখ্যা যেমন স্বল্প লোকসংখ্যার বিভাজনও তেমনি অসমানুপাতিক। সেই প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি আমাদের জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ বসবাস করে আসছে গ্রামে। গ্রামই আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পাদপীঠ। আমাদের জীবন ঘরানার মৌল বৈশিষ্ট্যটি খুঁজে পাওয়া যায় গ্রামেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাম্প্রতিককালে নগরসমূহ হয়ে উঠেছে সবকিছুর ধারক ও নিয়ন্ত্রক। আয়তন ও সংখ্যার দিক থেকে সামান্য হলেও বিশাল গ্রাম-সাম্রাজ্যের চালিকাশক্তি এখন শহরের হাতে। তাই গ্রামের মানুষ তাদের জীবনের দিকনির্দেশনা পাবার জন্য তাকিয়ে থাকে শহরের দিকে। শহরের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে চেষ্টা চালায় আপন জীবন ও জনপদের উন্নতি সাধনের। এই প্রচেষ্টার ফল সবসময় যে ইতিবাচক হয় তা নয়। কখনও কখনও ঘটে দারুণ নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া। শামসুদ্দীন আবুল কালাম তাঁর ‘পথ জানা নাই’ গল্পটিতে সেই অনাকাঙ্ক্ষিত নেতিবাচক পরিচয়টিকেই উদ্ঘাটন করেছেন। শামসুদ্দীন আবুল কালাম তাঁর ‘পথ জানা নাই’ গল্পে নাগরিক সভ্যতার নেতিবাচক দিকটিকেই মুখ্য করে তুলেছেন। গ্রামকে তিনি দেখেছেন শান্তি ও স্বস্তিময় জীবনের অধিষ্ঠানভূমি হিসেবে। সম্পদের প্রাচুর্য সেখানে নেই, নেই আলো ঝলমল জীবনের গরিমা; কিন্তু রয়েছে অনাবিল প্রশান্তি আর আদিম সরলতা। কঠোর পরিশ্রমে এখানকার মানুষ ফসল ফলায়। জমি ও নারীর অধিকার নিয়ে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতেও পিছুপা হয় না। তবে সংঘাতের চেয়ে সহমর্মিতার পরিমাণই এখানে বেশি। তাই পরিবার থেকে শুরু করে গোটা সমাজ পারিপার্শ্বিকতার কোথাও আন্তরিকতা বা হৃদ্যতার কোন ঘাটতি পড়ে না। দক্ষিণ বাংলার মাউলতলা নামে এক নিভৃত গ্রামের পটভূমিতে যে জীবনচিত্রকে গল্পকার উপস্থাপন করেছেন তা এক প্রীতিময় আবেগ ও স্নিগ্ধতায় সর্বাঙ্গ পরিপুষ্ট। পক্ষান্তরে নাগরিক জীবনের যে পরিচয় গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে তার প্রায় সবটুকুই কালিমায় লিপ্ত। নতুন রাস্তা তৈরি হওয়ার পর গহুরালি যখন তার সবক’টি জামা একসাথে গায়ে চাপিয়ে, চোখে মুখে তেল মেখে প্রসাধন চর্চিত হয়ে শহর ভ্রমণে যায় তখন সেখানকার মানুষজনের চালচলন, জীবনযাত্রা, ধনঐশ্বর্য দেখে প্রথমে সে বিস্মিত হয়। কিন্তু তার পরপরই হতাশ হয়ে পড়ে। যখন দেখে ‘তাহার মত দীন দরিদ্রের প্রতি সকলেই ভ্রুক্ষেপহীন। দুইদণ্ড আসিয়া এখানে কেহই তো তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করে না। শহর গহুরালিকে হতাশ করলেও পয়সার মূল্য সম্পর্কে তাকে সজাগ করে তুলেছিল। সে তাই গ্রামে ফিরে এসেছিল অর্থের প্রতি এক নতুন জাগা মমত্ববোধ সাথে নিয়ে। পরবর্তীতে তাই সে তার জীবনকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত করেছে অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টায়। গ্রামের তরিতরকারী, শাকসব্জী যা সে পেয়েছে হাতের কাছে, তা-ই শহরে বয়ে নিয়ে গেছে বিক্রি করে অর্থ প্রাপ্তির আসায়। তার এই প্রবণতা লক্ষ করে একদিন তার বউ হাজেরা তাকে পরিহাস করে বলেছিল “যা আরম্ভ করলা, শেষকালে আমাগোও না বাজারে লইয়া যাও।” পয়সার দামে যেখানে সবকিছু বিকিয়ে যায় সেই নাগরিক সভ্যতার হাতে ক্রীড়নক স্বামীর প্রতি হাজেরা খানিকটা ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিতে তাকালেও শেষাবধি সে নিজেই বলী হয়ে গেছে সেই সভ্যতার আগ্রাসী থাবার কাছে। শহুরে সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে পরিবর্তন শুধু গহুরালির জীবনেই আসে না, আসে গোটা গ্রাম্য জীবনেই। তবে সেই পরিবর্তনের প্রায় সবটুকুই নেতিবাচক। সামান্য কারণেই মানুষ মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে মেতে ওঠে। বহু দূরের যুদ্ধের উত্তাপ এসে লাগে তাদের গায়ে। শোনা যায় মন্বন্তরের পদধ্বনি। লেখকের ভাষায়, “চালডালের দাম, বাড়িল। দাম চড়িল সব জিনিসের। কমিল কেবল জীবনের। ধীরে ধীরে এই সড়ক বহিয়াই আসিল মন্বন্তর। আসিল রোগব্যাধি, চোরাবাজার আর দুর্নীতির উত্তাল জোয়ার। সুশাসনে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী আসে এই পথ বাহিয়া, আবার ঘুষ পকেটে লইয়া ফিরিয়া যায়। শহরের সাহেবের বাবুর্চিখানায় কাজ করে যে লুৎফর, তাহার সহিত সোমত্তকন্যা কুলসুম উধাও হইয়া যায়। লড়াই ফেরৎ ইউসুফের স্ত্রী কঠিন স্ত্রীরোগে হাত-পা-মুখে ঘা লইয়া শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। আর আসে তরিতরকারী, কাঠ, মুরগী-হ্যানোত্যানো নানা জিনিস কিনিতে মিলিটারীর দালাল।” এই দালালের হাত ধরেই গহুরালির জীবনে আসে চরম সর্বনাশ। এক সকালে ঘুম থেকে উঠে গহুরালি তার বউ হাজেরাকে আর খুঁজে পেল না। অনেক খোঁজাখুঁজি করে জানতে পারে যে তার বউ সই দালালের সাথে শহরের দিকে চলে গেছে। অন্তরে বাইরে নিঃস্ব গহুরালির জন্য তখন অবরুদ্ধ আক্রোশ বুকে নিয়ে শহরের সাথে সংযোগ সাধনকারী নতুন রাস্তাটিকে কুপিয়ে কুপিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা ছাড়া আর কিছুই রইল না তার করার। অবিমিশ্র ভালো বা মন্দ বলে কিছু নেই। যে কোন জিনিসের ভালো দিকের পাশাপাশি তার কিছু মন্দ দিকও চোখে পড়ে। গ্রামীণ সভ্যতা সংস্কৃতির যেমন নেতিবাচক দিক আছে তেমনি আছে তার ইতিবাচক পরিচয়ও। ঠিক তেমনি শহুরে সভ্যতার যেমন মন্দ দিক আছে তেমনি আছে তার ভালো দিকও। কিন্তু ‘পথ জানা নাই’ গল্পে লেখক শহুরে জীবন ও নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার শুধু নেতিৱাচক দিকটিকেই বড় করে দেখিয়েছেন। এ জীবনের প্রতি শুধু তার কটাক্ষই বর্ষিত হয়েছে। প্রকাশ পায়নি সামান্যতম ভালোবাসা কিংবা অনুরাগ।
পথ জানা নাই’ গল্পটি বর্তমান নগরকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতি তীব্র কটাক্ষ কি হেনেছে”- উক্তিটির আলোকে ‘পথ জানা নাই’ গল্পের মূলবক্তব্য নিজের ভাষায় লেখ।
পরবর্তী পরীক্ষার রকেট স্পেশাল সাজেশন পেতে হোয়াটস্যাপ করুন: 01979786079
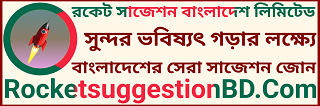
Leave a Reply