অথবা, ‘নয়নচারা’ গল্পের গঠনকৌশল উপস্থাপন কর।
অথবা, দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতায় ‘নয়নচারা’ গল্পের শিল্পপ্রকরণে যে অভিনবত্ব এসেছে তা ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : সমাজ সচেতন কথাসাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১) সৃষ্টিশীল সত্তার সাফল্য, খ্যাতি ও সিদ্ধি মূলত ঔপন্যাসিক হিসেবে। জীবন সন্ধানী এই শিল্পী ব্যক্তিজীবন ও সমাজসমস্যাকে করেছেন তাঁর সৃজনকর্মের উপজীব্য। তাঁর রচনায়। উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার, মূল্যবোধের অবক্ষয়, মানব মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতি। জাবন নিষ্ঠা, আধুনিক শিল্প প্রকরণ, তীব্র শৈল্পিক সচেতনতা, সংযম ও পরিমিতিবোধ তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভার মূল বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও ছোটগল্প এবং বাংলা নাট্যসাহিত্যেও তিনি নতুন ধারার পথিকৃৎ। দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে গ্রাম থেকে শহরে আসে জীবিকার অন্বেষণে। কিন্তু জীবিকার কোন সন্ধান না পেয়ে ‘নয়নচারা’ ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে ‘নয়নচারা’ গল্পটি রচিত। নয়নচারা একটি গ্রাম। এই গ্রামের আমু, ভুতো, ভূতনি আমুর ক্ষুধাতাড়িত অবসন্ন দেহখানি এক মুঠো ভাতের আশায় শহরের অলিগলি ঘুরে ফিরে। কোনো দিন তারা দুটো খেতে পেলেও তা জীবনধারণের জন্যে অসম্ভব হয়ে পড়ে। শহরে আমুর মতো দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষেরা শহরের অলিতে-গলিতে দুমুঠো খাদ্যের অন্বেষণে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করে। আমুর মনে হয় এক বিশাল অন্ধকার যেন হিংস্রতায় পাশবিক ইচ্ছায় নিষ্ঠুর ভাবে-গ্রাস করার জন্য তার দিকে এগিয়ে আসছে। এই শহরে আমুর মতো ক্ষুধাতাড়িতেরা মর্মান্তিকভাবে পরাজিত, প্রতিবাদ কিংবা প্রতিরোধ অসম্ভব। কেননা দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসাচ্ছিত নির্দয় সময়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে চারিদিকে মৃত্যুর যে ছায়া নেমে আসে তা থেকে আমুদের মুক্তি নেই। শহরের পরিবেশ গ্রাম থেকে আগত বুভুক্ষুদের জন্য কোনো ধরনের নিরাপত্তা বিধান করতে চরমভাবে ব্যর্থ। আমুরা শহরে মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে অন্নের নিরাপত্তা ছাড়া কোনো নিরাপত্তাই কামনা করেনি। কিন্তু তারপরেও দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষগুলো দারুণভাবে পরাজিত হয়ে অন্নহীন অবস্থায় খড়কুটোর মতো রাজপথে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে- তাদের চোখে ভেসে ওঠে শুধু মায়া-
মমতা জড়ানো ‘নয়নচারা’ গ্রামের কথা। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ অথবা মহামারর কালে মানুষ পরিণত হয় পণ্য কিংবা আবর্জনায়। তারপরেরও ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও মানুষের মনোবীণায় বেজে ওঠে হারানো সুখস্মৃতি। তাই আমুদের অন্তর্জগৎ ভরে ওঠে নয়নচারাকে ঘিরে। নয়নচারা গ্রাম ছিল আমুদের জীবনীশক্তি। তাই শহরের ফুটপাতে তারা খড়কুটোর মতো পড়ে থাকলেও ‘ঘনায়মান কালো রাতে জনশূন্য প্রশস্ত রাস্তাটাকে ময়ূরাক্ষী নদী বলে কল্পনা করতে বেশ লাগে।’ আমুর মতো আরো অনেকে খাদ্যের অন্বেষণে শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে চলেছে। তাদের অনন্ত ছোটাছুটি মৃত্যু ছাড়া থামে না । ফুটপাথের ধারে কেউ বেদনায় গোঙাচ্ছে, কেউ বা নিঃশব্দে ধুঁকছে। এ থেকে পালিয়ে বাঁচার কোন রাস্তার সন্ধান তাদের জানা নেই। আমুর ধারণা সেও অন্যদের মতো মৃত্যুর সদর দরজায় এসে পৌঁছেছে। এ-সময় প্রাণহীন দরজা খুলে একটি মেয়ে আমুকে ক্ষুধা নিবৃত্তির অন্ন জোগায়। আমু ত্রস্তভঙ্গিতে কাপড়ের প্রান্ত মেলে ধরে খাবারটুকু গ্রহণ করে এবং মেয়েটির কাছে জানতে চায় : নয়নচারা গাঁয়ে কি মায়ের বাড়ি?
মেয়েটি কোনো উত্তর দিল না। শুধু একটু বিস্ময় নিয়ে কয়েক মুহূর্ত তার পানে চেয়ে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।” ‘নয়নচারা’ গল্পে ব্যবহৃত চেতনাপ্রবাহরীতি, আমুর স্মৃতিময় অনুষঙ্গ, দুর্ভিক্ষতাড়িত আমু গ্রাম থেকে শহরে এলেও নগর তার অনাত্মীয়, গ্রামীণ স্বচ্ছলতা ও শান্তিই তার অনিষ্ট। আমুর এ স্মৃতিচারী অনুভূতিময়তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন গল্পকার আমুর চেতনাপ্রবাহরীতির মাধ্যমে “লালপেড়ে শাড়ি ঝলকাচ্ছে; রক্ত ছুটছে। যেমন করিম মিয়ার মুখ দিয়ে সেদিন ফিনকি দিয়ে ছুটেছিল রক্ত। – – হঠাৎ দুটি পয়সা দিয়ে চলে গেলো রক্ত ঝলকিয়ে। কিন্তু একটা কথাও ও কী ভেবেছে যে তার মাথায় সাজানো চুল তারই? আমু কী জানে না- আসলেও চুল কার। ও চুল নয়নচারা গাঁয়ের মেয়ে ঝিরার মাথার ঘন কালো চুল।” মেয়েটি গল্পে একাধিক চরিত্রের সমাগম ঘটলেও আমু এ গল্পের প্রধান চরিত্র। আমুর দুর্ভিক্ষ কবলিত অবস্থার কথা বলতে গিয়ে গল্পকার একাধিক ঘটনা এবং চরিত্রের সমাগম ঘটিয়েছেন।
পরিমিতিবোধ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র শিল্পচেতনার একটি বড় বৈশিষ্ট্য। তিনি তাঁর গল্পের বর্ণনায় পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ গল্প বর্ণনার ক্ষেত্রে অধিকাংশ গল্পেই সর্বোজ্ঞ লেখকের প্রেক্ষণ বিন্দু ব্যবহার করেছেন। তবে কখনো কখনো ব্যক্তির প্রেক্ষণ বিন্দুও প্রাধান্য পেয়েছে । ‘নয়নচারা’ গল্পটি সর্বোজ্ঞ লেখকের প্রেক্ষণ বিন্দু থেকে বর্ণিত হলেও প্রধান চরিত্র আমুর অর্থাৎ উত্তম পুরুষের প্রেক্ষণ বিন্দুতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন— “নদীতে জোয়ার না ভাটা? মনে হচ্ছে ভাটা, এবং এ ভাটাতে ভেসে যাবার প্রবল ইচ্ছে তার।” ‘নয়নচারা’ গল্পে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ দৃশ্যগুণময় পরিচর্যা এবং পৌনঃপুনিকভাবে ছবি এঁকে বক্তব্য উপস্থাপনে আগ্রহী ও উৎসুক । যার ফলে গল্পের ভাষা হয়েছে চিত্রকল্পময়। যেমন- “ময়ূরাক্ষীর তীরে কুয়াশা নেমেছে। স্তবদ্ধ দুপুর শান্ত নদী। দূরে একটি নৌকার খড়তাল ঝমঝম করছে আর এধারে শ্মশান ঘাটে মৃতদেহ পুড়ছে।”এ গল্পে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ আধুনিক সাহিত্যের সুরিয়ালিস্টিক পরিচর্যার ব্যবহার করেছেন। যেমন- “আগুনটা দুলছে না তো যেন হাসছে; আমুরা যখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় কঁকায় তখন পথ চলতি লোকেরা আলাদা অপরিচিত দুনিয়ার কোনো অজানা কথা নিয়ে হাসে, এ-ও যেন তেমনি হাসছে।” আলোচ্য গল্পে দুর্ভিক্ষ বহির্বাস্তবতা হলেও লেখক আমুর মনোজগৎ বা অন্তর্বাস্তবতার দিকেই বেশি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। লেখকের লেখনীতে মানুষের অনশনরত মন, অন্ধকারের চিত্র মানুষগুলোর মনোজাগতিক দিককে কিভাবে পঙ্গু করে তা স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন প্রাণময় ভাষা ব্যবহার করে। যেমন- “চারিদিকে অন্ধকার সব শান্ত, নীরবতা পাখাগুটিয়ে নিশ্চল হয়ে রয়েছে, আর জমাট বাঁধা ঘনায়মান পর্বতের কালোরাত্রি পর্বতের মত দীর্ঘ, বৃহৎ ও দুর্লঙ্ঘ্য।” তাছাড়াও লেখক গল্পের পরিচর্যার ক্ষেত্রে উপমা, পরাবাস্তবতা, চিত্রকল্প, অলংকারময় ভাষা ব্যবহার করে মানুষের মনোজাগতিক দিক প্রকাশিত হয়েছে। যেমন- “সারা আকাশ আমি বিষাক্ত রুক্ষ্ম জিহবা দিয়ে চাটব, চেটে-চেটে তেমনি নির্মমভাবে রক্ত ঝরাব সে- আকাশ দিয়ে কে তুমি, তুমি কে?” ‘নয়নচারা’ গল্পের সামগ্রিক আলোচনা থেকে এটাই স্পষ্টত বলা যায় যে, এগল্পে গল্পকার দুর্ভিক্ষের বিভীষিকাময় পরিবেশ অঙ্কনে সচেষ্ট ছিলেন। চেতনাপ্রবাহরীতির সাধারণত যে দুটি ধারা (আত্মবিশ্লেষণ রীতি ও অনুচ্চার মনোকথন রীতি) তা তিনি আলোচ্য গল্পে ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে লেখক চরিত্রের বাইরে থেকে মনোকথনরীতিতে আমুর অস্পষ্ট ভাবনা, অনুভূতি, স্মৃতিময়তা, যন্ত্রণাকাতর পরিবেশ, দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের দুর্বিষহ জীবনযাপন, শহরের চাকচিক্যময় দৃশ্য অঙ্কনের মধ্য দিয়ে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা উপস্থাপন করেছেন। তাছাড়া ভাবে, ভাষা, চরিত্র নির্মাণ এবং আধুনিক শিল্পকৌশল ব্যবহারের দিক থেকে ‘নয়নচারা’ গল্পটি সার্থক।
নয়নচারা’ গল্পের বিষয় ও শিল্পকৌশল আলোচনা কর।
পরবর্তী পরীক্ষার রকেট স্পেশাল সাজেশন পেতে হোয়াটস্যাপ করুন: 01979786079
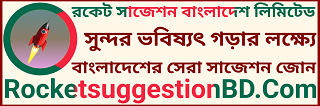
Leave a Reply