অথবা, দার্শনিক কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়নমূলক আলোচনা কর।
অথবা, দার্শনিক কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা কর ।
উত্তর।। ভূমিকা : দর্শনের যেমন সাহিত্যেরও তেমনি উপজীব্য জগৎ ও জীবন। উভয়ের লক্ষ্যও এক ও অভিন্ন, যদিও আলোচনার পদ্ধতিগত বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- দর্শন অগ্রসর হয় যৌক্তিক মূল্যায়ন ও বিচারবিশ্লেষণের পথে, আর সাহিত্য বিশেষত কাব্য প্রধানত নির্ভর করে অনুভব ও হৃদয়াবেগের উপর। দর্শন তার বিষয়বস্তুকে পরিমাপ করে যুক্তির নিরিখে, আর কাব্যের আবেদন আবেগ-আপ্লুত হৃদয়তন্ত্রীর দরবারে। কিন্তু তাই বলে উভয়ের সম্পর্ক দূরত্বের সম্পর্ক নয়, বরং খুবই নিকট ও নিবিড়। তাইতো দেখা যায়, পৃথিবীর আদি রচনাবলির একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যুগপৎ স্বীকৃতি পেয়েছে সাহিত্য ও দর্শন বলে। বেশকিছু লেখক কবি হয়েও নন্দিত হয়েছেন দার্শনিক হিসেবে। এ হিসেবেই রবীন্দ্রনাথ স্বীকৃতি পেয়েছেন দার্শনিক কবি হিসেবে।
দার্শনিক কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি : যিনি শুধু কবি, দার্শনিক নন তিনি তাঁর কাব্যে জগৎ ও জীবনের কিছু বিবরণ দেন মাত্র। আর যিনি একাধারে কবি ও দার্শনিক, তিনি তাঁর কাব্যে জগৎ ও জীবনের নিছক বর্ণনা দেন না, ছন্দ-যুক্তির সমন্বয়ে হাজির করেন এক চমৎকার ব্যাখ্যা। এ প্রসঙ্গে ইংরেজ সাহিত্যিক S. T. Colridge বলেছেন, “No man was ever yet a great poet without being at the same time a profound philosopher.” অর্থাৎ, যিনি একজন বড়মাপের কবি তিনি একই সাথে একজন প্রগাঢ় দার্শনিক না হয়ে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ এমনই একজন দার্শনিক কবি যিনি জগৎ ও জীবনের গূঢ় রহস্য উন্মীলিত করেছেন তাঁর বিভিন্ন কাব্যের মাধ্যমে। নিম্নে দার্শনিক কবি হিসেবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করা হলো :
রবীন্দ্রনাথের বেদান্ত দর্শন : বেদের সর্বশেষ অংশ বলে উপনিষদের অপর নাম বেদান্ত দর্শন। জীবন ও জগতের সত্যোপলব্ধির অদম্য প্রচেষ্টা ও দার্শনিক বিশ্লেষণ নিয়ে খ্রিস্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে ভারতীয় দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বেদান্ত দর্শনের সূচনা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজীবন ও জগতের বহুত্বের মধ্যে নিজেকে বিকশিত করে নিখিলের আনন্দ যজ্ঞে অংশ নিয়েছেন। ধর্ম সম্পর্কে তিনি বলেছেন, পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবোধ। তিনি বলেছেন, ব্রহ্মের আনন্দের জন্যই জগৎ ও জীবের সৃষ্টি। তাঁর মতে, অসীমের মধ্যে সীমা ও প্রেম নেই; অসীম সীমার নিবিড় সঙ্গ লাভ করতে চায়। রবীন্দ্রনাথ পরমেশ্বর জীবের সংসর্গ কামনা করেন। তাঁর মতে, জীব ও জগৎ ছাড়া ব্রহ্ম অপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতাঞ্জলিতে বলেছেন,
“আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী
তারি সাথে, প্রভু, মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।”
ঈশ্বর যেমন জীবের মিলন পিয়াসী জীবও তেমন পরমাত্মার জন্য তৃষ্ণার্ত। তাইতো তিনি লিখেছেন,
“পুষ্প যেমন আলোর লাগি
না জেনে রাত কাটায় জাগি
তেমনি তোমার আশায় আমার
হৃদয় আছে ছেয়ে।”
রবীন্দ্রনাথের রহস্যবাদ : সকল শ্রেষ্ঠ দার্শনিকই রহস্যবাদ বা এ রহস্যময় পৃথিবীর আত্মজিজ্ঞাসা তাঁদের তন্ময়তার বাণীর মাধ্যমে আমাদের নিকট বিবৃত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবন প্রভাতেই জানতে পেরেছেন যে, পার্থিব সংকীর্ণতার মায়ামোহ কারাগার প্রকাণ্ড আকার হয়ে তাঁকে চারদিকে বেষ্টন করেছে। তাই তিনি বলেছেন-
“ওরে চারিদিকে মোর
একি কারাগার ঘোর,
ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর,
ওরে আজ কি গান গেয়েছে পাখি,
এসেছে রবির কর।”
নবজীবন ও অন্তর্জীবন বলতে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন মনুষ্যত্বের উপলব্ধি। তিনি বলেছেন, মননের দ্বারা আমরা যে অন্তজীবন লাভ করি তার মূল লক্ষ্য পরমার্থ। জীবন প্রভাতেই প্রাণ নির্ঝরের পার্থিব মায়ামোহের স্বপ্ন হতে রবীন্দ্রনাথের অব্যাহতি লাভ, এটা তার কবি জীবনের এক আশ্চর্য ঘটনা। এ নবজীবন প্রাপ্তিকে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর ভাষায়, “তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া।”
রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ : বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশে যাঁদের কণ্ঠে মানবতার জয়গান শোনা যায় তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। সমাজের উচ্চাসনে আসীন হয়েও তিনি অবহেলিত উৎপীড়িত ও সর্বহারা মানুষের কথা ভেবেছেন। কবির অকৃত্রিম সহানুভূতি ও সহমর্মিতা তাঁর অসংখ্য কবিতা ও গানে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর প্রথম দিকের কাব্যগুলোর মধ্যে চৈতালী’ কাব্যের কবিতাগুলোতে মানবতার চরম উন্মেষ ঘটেছে। মানবতার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে আবিষ্কৃত করেছেন। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে জেনারেল ডায়ারের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদস্বরূপ কবি ইংরেজদের ‘নাইট’ উপাধি বর্জন করেন। মানবপ্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ বেলায় উঁচু বেদীর সোনার সিংহাসন থেকে নেমে ধূলিমলিন মানুষের সতীর্থ হয়েছেন। তাইতো তিনি তাঁর কবিতায় উল্লেখ করেন-
“মূক যারা দুঃখে সুখে
নতশির যারা বিশ্বের সম্মুখে
ওগো গুণী
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।”
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন : বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রতীচ্যের শিক্ষাদর্শনকে পুরোপুরি খাপখাওয়ানো সম্ভব নয় বলে প্রাচ্যের অনেক দার্শনিকই প্রতীচ্যের শিক্ষাদর্শনকে গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করেন। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন কবিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাদ শিক্ষার্থীকে প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে শিক্ষা গ্রহণ করার কথা বলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মানুষের আত্মিক শক্তি ও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর
উচ্চমর্যাদা আরোপ এবং তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে পরিস্ফুট করে সত্যিকার অমৃতরূপের উন্মোচন। শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ মনের স্থান দিয়েছেন অতি উচ্চে। তিনি শিক্ষার্থীর মনকে যেমন সক্রিয় রাখতে চেয়েছেন, তেমনি তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেও সক্রিয় রাখতে চেয়েছেন। অর্থাৎ তিনি শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয়কে সজাগ ও সক্রিয় রাখার কথা বলেছেন এবং জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ নির্ভর করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, শিক্ষার্থীকে অল্প অল্প করে শেখাতে হবে এবং তারা যতটুকু
শিখবে ততটুকুই প্রয়োগ করতে শিখবে।
মূল্যায়ন : উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে রবীন্দ্রনাথ বিচারবিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন দার্শনিক মত গড়ে তুলেছেন একথা অবশ্য হলফ করে বলা যাবে না; কারণ তিনি মূলত একজন কবি, আর কবি হিসেবে তাঁর রচনার মূল উপাদান ও আলোচনার পদ্ধতি দার্শনিক বিচারবিশ্লেষণের নয়; অনাবিল হৃদয়াবেগ ও অপরোক্ষ অনুভূতি। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মত যৌক্তিক প্রয়োগ পদ্ধতির আশ্রয় নেননি; তাঁর কবি হৃদয়ে ভেদবুদ্ধি বা যুক্তি বিচারের চেয়ে অনুভূতিই ছিল প্রবল। তবে একথাও বলা যাবে না যে, হৃদয়াবেগের চাপে কবিগুরু দার্শনিক যুক্তির পথ পরিহার করেছেন। বরং সসীম অসীমের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি যে কবিতার অবতারণা করেছেন তা যুগপৎ স্বীকৃত অনবদ্য কাব্য ও যথার্থ দর্শন হিসেবে। উপনিষদের ব্রহ্মের কথাই বলি, ভগবানের কথাই বলি কিংবা তার জীবনদেবতার কথাই বলি, এদের সবাইকেই রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন মানুষের মনে ও প্রকৃতিতে অনুস্যূত সত্তারূপে। অর্থাৎ রবীন্দ্র সাহিত্য ও দর্শনে হৃদয়াবেগ ও যুক্তি বিচারের অপরোক্ষ অনুভূতি ও ভেদবুদ্ধির একটা সুন্দর সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কবিতায় একদিকে যেমন উপস্থিত কবিহৃদয়ের সুদৃঢ় প্রেরণাদায়ক অনুভূতি ও বিশ্বাস, তেমনি আভাস পাওয়া যায় আদর্শবাদী জীবনদর্শনের রূপ-স্বরূপ ও অন্তঃসারের।
উপসংহার: পরিশেষে বলা যায় যে, দর্শনের পথ যুক্তির পথ সন্দেহ নেই। কিন্তু কেবল যুক্তি দিয়ে মনকে নিঃসংশয়, বিধামুক্ত ও পরিতৃপ্ত করা যায় না। এজন্যে প্রয়োজন অখও অনুভূতি ও অনাবিল হৃদয়াবেগ, যা-কিনা কাব্যসাহিত্যের মূল অবলম্বন। যে রচনায় একদিকে সাহিত্যিক আনন্দ অনুভূতি এবং অন্যদিকে দার্শনিক যুক্তি বিচারের সার্থক সমন্বয় ঘটে, সে রচনাই সুসাহিত্য ও প্রকৃত দর্শনের এবং সেই কাব্যসাহিত্যের রচয়িতাই লাভ করেন দার্শনিক কবির মর্যাদা। আর এ মর্যাদাসম্পন্ন একজন অন্যতম দার্শনিক কবি হচ্ছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
দার্শনিক কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন কর।
পরবর্তী পরীক্ষার রকেট স্পেশাল সাজেশন পেতে হোয়াটস্যাপ করুন: 01979786079
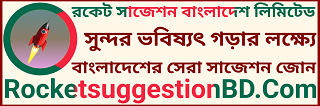
Leave a Reply